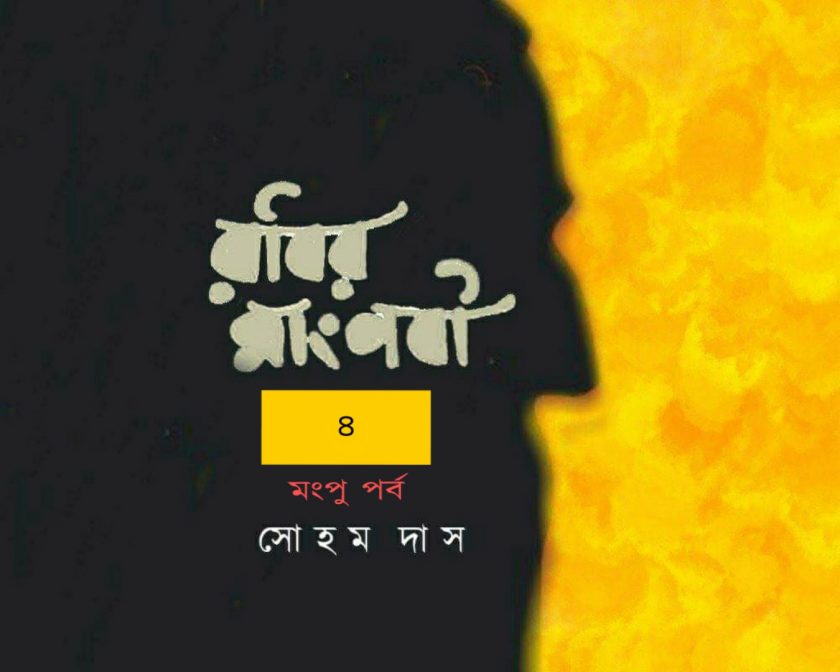
মংপু পর্ব
৩
মংপু-মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ

‘…এই কাচের ঘরটা বুঝি আমার লেখবার? এ তো খুবই ভাল, একেবারে উত্তম বলা যেতে পারে। এ চৌকিতে সকালবেলা বসব আর রোদ্দুর এসে পড়বে কাচের ভেতর দিয়ে। তোমার ঐ বৃহদাকার বনস্পতির পাতার ফাঁক দিয়ে শতধারায় ঝরে পড়বে সকালবেলার আলো, ভোরের সেই রৌদ্রস্নানটি আমার কত সুন্দর হবে।’
বারান্দা দিয়ে ঢুকে বাঁদিকের প্রান্তে যে কাচঘেরা পড়ার ঘরের কথা উল্লেখ করেছি আগের পরিচ্ছেদে, এই প্রশংসা সেই ঘরটাকে নিয়েই, অন্তত বর্ণনা তো একেবারে মিলে যাচ্ছে। ছোট্ট ঘরটার দরজা, জানলা ধবধবে সাদা রঙে শোভিত। ফলে কাচের মধ্যে দিয়ে আলো ঢুকে সারা ঘরে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। রৌদ্রস্নানের উপযুক্তই বটে। এই ডেস্কে বসে লিখতেন আর সেগুলো কপি করতে হতো মৈত্রেয়ী দেবীকে, যাকে কখনও ডাকতেন সুমিত্রা, কখনও সীমন্তিনী, কখনও সুনয়নী, আবার কখনও মাংপবী।

প্রথমে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এ তথ্যটা শিশিরের কাছ থেকেই পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যখন আসতেন, এই বারান্দা এমন ঘেরা ছিল না, তা ছিল উন্মুক্ত। ফলে সুদূরের পিয়াসী কবি বাংলো-চত্বরের সবুজ ছোট মাঠটি এবং সামনের সবুজ পাহাড়ি ঢাল দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে যান। প্রথমবার যখন মংপু এলেন, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ৬ই জুন, সেদিন বেলা গড়িয়ে গেছে। ‘তখন রোদ চারদিকের ধোয়া সবুজের উপর ঝিলমিল করছে, শেষ বেলাকার রোদের সুন্দর শান্ত হাসি।’ পাহাড়ে আলোর খেলা দেখে শিশুর মতো আনন্দিত হয়েছিলেন আলোকময় কবি।
প্রথমবার এসে মাত্র তিনদিন ছিলেন মংপুর বাংলোয়। তার আগের কটা দিন তো আগেই বলেছি, মংপু থেকে বেশ অনেকটা উঁচুতে সুরেল বাংলোয় ছিলেন। সেসময় বর্ষার আগমন শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই একদিন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, কুয়াশা কেটে ঝলমলে নীল আকাশ দেখা দিয়েছে, আর তা দেখে জন্ম-রোমান্টিকতা চাগাড় দিয়ে উঠবে না তা কি আর হয়? মন্তব্য করেছিলেন-‘এ যে বসন্তকাল, তেমনি ঝুর ঝুর ক’রে বাতাস দিচ্ছে, অসময়ে এ বসন্ত ভারী সুন্দর।’

রবিঠাকুরের এই মংপু-পদার্পণে কাগজে ফলাও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি অনুযায়ী, সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিনকোনা ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। এটা ব্যঙ্গ করে, না সত্যিই এমন মনে করেছিলেন সংবাদদাতারা তা অবশ্য জানা যায়নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়ার বিপুল চাহিদা সেসময়ে। সাধারণ লেখা থেকে শুরু করে যেকোনো পণ্য অবধি। তিনি মজা করে বলতেন-‘আমার আবার ঐ এক গেরো, সঙ্গে আছেন এসোসিয়েটেড প্রেস,…সার্টিফিকেটের জ্বালায় আর নামকরণের জ্বালায় পেরে উঠিনে।’ আসলে ঋষিপ্রতিম মানুষটির সম্পর্কে মানুষের বদ্ধমূল ধারণাই ছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হেন কোনও জিনিস নেই যা তিনি জানেন না। যতই তিনি ‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি’ লিখে থাকুন, সাধারণ মানুষ তাঁকে সর্বজ্ঞ বলেই মনে করত। সেক্ষেত্রে, সিনকোনা চাষের ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে যাওয়ার কথা লেখা ব্যঙ্গ করে নাও হতে পারে।
কবি কালিম্পঙে ফিরে গেলেন ৯ই জুন। বিশ্বভারতীর কাজের জন্য রাজপুরুষরা এসেছিলেন সেখানে। হঠাৎ করেই চলে যেতে হওয়ায় মৈত্রেয়ী দেবীর স্বাভাবিকভাবেই মনখারাপ হয়ে যায়। কবি আশ্বস্ত করে যান, কাজ সেরে আবার আসবেন। কিন্তু সেবার আর সেটা হয়নি। এখানে সামান্য একটি ব্যক্তিগত ভাবনা ভাগ করে নিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের এই মংপু আসা-যাওয়ার দিন-তারিখের পরিসংখ্যান আমার সম্পূর্ণ মনে না থাকলেও প্রথমবার মংপু থেকে চলে যাওয়ার এই তারিখটি আমি কোনোদিন ভুলব না। কারণ এই দিনটি আমার জন্মদিন।
কবি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে মৈত্রেয়ী দেবীও গিয়েছিলেন কালিম্পঙে। তারপর মংপুতে তাঁর আত্মীয় আসায় তাঁকে কিছুদিনের জন্য মংপুতে চলে আসতে হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ মনস্থির করেন যে, এবার শান্তিনিকেতন ফিরবেন। ২রা জুলাইয়ে মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখছেন-
‘কল্যাণীয়াসু
কিছুদিনের জন্য এখান থেকে অন্তর্ধান করব-বৌমাকে রেখে গেলেম প্রতিভূ, অতএব ফিরব তাতে সন্দেহ নেই। বৌমা কাল থেকে জ্বরে পড়েছেন। আজ সকালে ভালো আছেন কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ না দেখে যেতে পারচিনে।
তোমাদের ঘরের আত্মীয় স্বজন চলে গিয়ে তুমিও বোধকরি ছুটি পেয়েছ। সর্ব্বসাধারণের কাছে আমি ছুটি নিয়েছি কাগজে পড়ে থাকবে। ইতি ২।৭।৩৮
স্নেহানুরক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’
 মংপুর প্রকৃতি, তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। ফুলের সমারোহ তাঁর চিত্ত চঞ্চল করত। মৈত্রেয়ী দেবীর ঘরে ফুল রাখার একটি বাঁশের পাত্র ছিল, সেটা রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দ ছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল-‘এই রকম জিনিসেই ফুল মানায় ভাল-শৌখিন দামী পাত্রে ফুলকেও যেন সাজতে চায়-একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি সেটা।’
মংপুর প্রকৃতি, তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। ফুলের সমারোহ তাঁর চিত্ত চঞ্চল করত। মৈত্রেয়ী দেবীর ঘরে ফুল রাখার একটি বাঁশের পাত্র ছিল, সেটা রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দ ছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল-‘এই রকম জিনিসেই ফুল মানায় ভাল-শৌখিন দামী পাত্রে ফুলকেও যেন সাজতে চায়-একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি সেটা।’
নীল জ্যাকারাণ্ডা ফুলের নামটি অমন বেরসিক হওয়ায় কবির মন্তব্য ছিল-‘এমন সুকুমার রূপে এমন দন্তবিমর্দিনী নাম।’ এইখানে আরেকটি তথ্য মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কবি বারবার বলতেন, ফুলের মধ্যে নীল রংটাই তিনি দেখতে পান বেশি এবং তাই ওই রংটাই তাঁর ভাল লাগে। এ প্রসঙ্গে রানী চন্দের ‘গুরুদেব’ বইয়ের একটি অংশে রয়েছে-‘গুরুদেব বলতেন তিনি নাকি রঙ-কানা, বিশেষ করে লাল রঙটা নাকি তাঁর চোখেই পড়ে না। অথচ দেখেছি অতি হালকা নীলও তাঁর চোখ এড়ায় না। একবার বিদেশে কোথায় যেন ট্রেনে যেতে যেতে তিনি দেখেছেন অজস্র ছোটো ছোটো নীলফুল ফুটে আছে রেল-লাইনের দুধারের ঘাসে। গুরুদেব বলতেন, আমি যত বউমাদের ডেকে ডেকে সে ফুল দেখাচ্ছি তারা তা দেখতেই পাচ্ছিলেন না। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম এমন রঙও লোকের দৃষ্টি এড়ায়।’

এই একই কারণে তাঁর আঁকা ছবিতে লাল রঙের প্রাচুর্যটা থাকত রীতিমত চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সহজে নীল রং দিতেই চাইতেন না। নিজের ভালো লাগাকে সহজে অন্য সকলের সাথে ভাগ না করতে চাওয়ার কার্পণ্য। মংপুর দেওয়ালে যে সব ছবি টাঙানো রয়েছে, তাতেও দেখেছি লালের ভাগ বেশি। বিশেষত সিনারি আঁকার ক্ষেত্রে আকাশের রঙে লাল, কমলা এসে মিশেছে সীমাহীনভাবে, কিন্তু নীলের প্রভাব সেভাবে প্রায় নেই বললেই চলে।
মংপুর ফুলের কথার ফেরা যাক। মৈত্রেয়ী দেবীর কন্যা মিষ্টু বা মিঠুয়া তখন খুব ছোট। রবীন্দ্রনাথ বলেন-‘তোমার কন্যা এই যে ফুলের দেশে প্রকৃতির কাছাকাছি মানুষ হচ্ছে এ খুব স্বাস্থ্যকর। শহরে মানুষের চাপে ইস্কুলের অত্যাচারে সে এক প্রাণ-বের-করা আবহাওয়া। আমাদের ওখানেও খোলা মাঠের মধ্যে খোয়াই-এর ওপর ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়ায়, বৃষ্টি নামলেই দল বেঁধে ভিজতে বেরিয়ে পড়ে। কী আনন্দ তাদের,-খুশি হবার সুযোগ পায় তারা।’ স্কুল নামক চার দেওয়ালের আবদ্ধ সংকীর্ণতাকে তিনি সেই যে শৈশবেই ত্যাগ করে এসেছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

চতুর্থ বার মংপুতে গিয়ে তাঁর অতি-সংক্ষিপ্ত স্কুলজীবনের ততোধিক সংক্ষিপ্ত দুটি ঘটনা বলেছিলেন। সেগুলো শুনলেই পরিষ্কার হবে, কেন তিনি এই ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ‘আমাদের সেই স্কুলে গিয়েই সারি সারি দাঁড়িয়ে twinkle twinkle little star, ভোরবেলায় টুইন টুইন লিটিল স্টার করে চিৎকার। বাবা,-সকালবেলায় কোথায় little star তাও জানিনে, মানে কি তাও বুঝিনে, শুধু চেঁচাচ্ছি, এত stupid! তারপর ঠেলে দিল পণ্ডিতের ঘরে। পণ্ডিত মশায়কে দেখলে পকেট থেকে আস্তে আস্তে আমসত্ত্ব বের করতুম, তাতে অনেকটা ঠাণ্ডা থাকতেন।’
সেই আমসত্ত্ব চুরি করে আনতেন তিনি আর

তাঁর দু’বছরের বড় ভাগ্নে সত্য (সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়; রবীন্দ্রনাথের বড়দি সৌদামিনী দেবী ও তাঁর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র)। কদিন বাদে আবার পণ্ডিতমশায়ের আবদার, কেয়া খয়ের আনতে হবে। সেও মামা-ভাগ্নেতে চুরি করে নিয়ে আসতেন কেবলমাত্র পণ্ডিতকে ঠাণ্ডা রাখবেন বলে।
বারান্দার কাঠের মেঝে বেশ ঠাণ্ডা। বেশ কয়েকজন মানুষের নিয়ত পদচারণায় একটা চাপা আওয়াজ উঠছে। আমি তার উপর বসে ভিজিটর্স বুকের পাতা ওল্টাচ্ছি। দরজার সামনে সুদীপ বসে কাজ দেখছে। খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই ঘটছে এক অবর্ণনীয় সময়-ভ্রমণ। এই বারান্দাতেই একদিন শালপ্রাংশু মহীরুহটি এসে বসতেন চৌকিতে। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে পায়ের ওপর চাদর বিছানো থাকত। সামনের ছোট মাঠ, পাহাড়ের সবুজ এসমস্ত ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হতো কোন সুদূরে! ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’-এই পড়েছি, সন্ধে নামলেই চৌকিতে এসে বসতেন। পাহাড়ের অন্ধকার দেহে একটি একটি করে আলো জ্বলে ওঠার দৃশ্য দেখতে দেখতে মুগ্ধ হতেন তিনি। ‘অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে, একাকার হয়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট দীপবর্তিকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্তা বহন করে আনছে।’ দুর্গম অরণ্যাবৃত অজানা পাহাড়েও মানবজীবনের সাবলীলতার রহস্য তাঁকে মুগ্ধ করত। মংপুর প্রকৃতির পাশাপাশি দূর পাহাড়ের অচেনা মানুষজনকে চিনতে চাইতেন তিনি। বলতেন-‘যাদের মধ্যে এসেছি, যাদের ওই দূরের রাস্তায় ঘোড়ার পিঠে বোঝা চাপিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছি তারা কেমন কাছে থেকে দেখতে চাই।’

এই আলো নিয়ে আরেকটি মজার ব্যাপার তাঁকে আমোদিত করত। সে আলো অবশ্য রহস্য-উদ্রেককারী নয়, সে আলো কোডের আলো। মংপুর মুখোমুখি পাহাড়, অর্থাৎ তাগদা যে পাহাড়ের গায়ে, সেখানে তখন দাশগুপ্ত পরিবার এসে রয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে যে রংলি রংলিওট চা বাগানের উল্লেখ করেছি, সেই রংলি রংলিওট আসলে এই তাগদাতেই। মংপুর বাংলোর অধিবাসীরা দাশগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলতেন সাংকেতিক আলোর মাধ্যমে। মৈত্রেয়ী দেবীকে যেমন সুমিত্রা বলে ডাকতেন, চিত্রিতা দেবীকে তেমন ডাকতেন সুচিত্রা বলে। এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে সুরসিক কবি মন্তব্য করেন-‘ও বাবা, এ তো ব্যাপার কম নয়! সুচিত্রা দেবী বিরহিণী বসে আছেন, আর এখান থেকে তাঁর ভগ্নীপতি আলোর দূত পাঠাবেন! ওহে ডাক্তার, এ যে মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গেল।’

ভোর থেকেই লিখতে বসতেন কবি। ওই কাচের ঘরে চলত লেখা। পাশেই বাগান। সেখানে ফুটে থাকা হলিহক, লিলি, জ্যাকারাণ্ডাদের মনমোহিনী রূপ। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার খটকা লাগছিল। আমি পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ কখনও জানলার ধারে বসে লিখতেন না। কারণ, লিখতে পারতেন না। প্রাকৃতিক শোভা তাঁকে চঞ্চল করে দিত, তাঁর মন চলে যেত সুদূরের পথ বেয়ে। তাহলে এখানে এত অপার্থিব সৌন্দর্যের সামনে বসে লেখায় মন দিতেন কীভাবে? তাহলে কাজে ডুব দিয়েই সমস্ত বাস্তবজগত-বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার ঐশ্বরিক যে ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন, এক্ষেত্রেও কি সেই ক্ষমতারই প্রকাশ?
মংপু তাঁকে কতটা টানত তার বড় প্রমাণই তো হচ্ছে, নির্জনতার কোলে আশ্রয় নিতে ভগ্ন শরীরেও বারবার ছুটে যাওয়া। মৈত্রেয়ীকে বলতেন-‘আমাকে এখানে একটা কাজ দাও না, একটা কুঁড়ে বেঁধে থাকি! আর উনি নিশ্চয় আমার শরীরের অবস্থা বুঝে হাল্কারকম কাজ দেবেন দয়া করে? বেশ থাকব চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে, ফরওয়ার্ড ব্লক নেই, নামকরণ নেই, ঈশ্বর দয়াময় কিনা আমার কাছে তার সার্টিফিকেট চাওয়া নেই!’

এটা মৈত্রেয়ীকে কবি বলেছেন দ্বিতীয়বার মংপু গিয়ে, অর্থাৎ ১৯৩৯-এর ১৪ই মে থেকে ১৭ই জুনের গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে গিয়েছিলেন যখন। ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি হয়েছে কিছুদিন আগেই। কবি মংপুতে আসার এগারো দিন আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুভাষযন্দ্র বসু তৈরি করেছেন তাঁর নিজস্ব দল। ২৯শে এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দেওয়ার চারদিনের মধ্যেই একক দক্ষতায় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার নজির বোধহয় বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাসে কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ সেসময় সুভাষচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। দুজনেই অতি ব্যস্ততার মধ্যেও সময় পেলেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিকবার আলোচনায় বসেছেন। সুভাষচন্দ্র তখন কয়েকবার শান্তিনিকেতন গিয়েছেন। কয়েক মাস আগেই শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের স্থায়ী ভাণ্ডার খোলা হয়। তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮। সুভাষচন্দ্র তখন কংগ্রেসের কাজে পাঞ্জাবে। তবু কাজ ফেলে কবির ডাকে দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য ছুটে না এসে পারেননি।

দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কলকাতায় কংগ্রেস ভবনের জন্য একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করেন সুভাষচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। পরে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ এবং অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস থেকে তাঁর বহিষ্কার কবিকে দুঃখিত ও একইসঙ্গে আশঙ্কিত করেছিল। সুভাষকে আবার কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে গান্ধীজীকে লেখা তাঁর চিঠির কথা সকলেই জানেন। সুভাষচন্দ্র এরপর যখন মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন, কবি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সেকাজে তাঁর সহায়তা করেন। মহাজাতি সদন নামটিও রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। এই মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান নিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর একটি আজীবন আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল, এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা উল্লেখ করছি।
মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান হল ১৮ই অগাস্ট, ১৯৩৯। তারিখটা কিন্তু অদ্ভুত রকমের লক্ষণীয়। ছ’বছর বাদে ভবনের প্রতিষ্ঠাতা চিররহস্যের আশ্রয় নিয়ে হারিয়ে যাবেন যে দিনটায়, সেদিনের তারিখটাও ১৮ই অগাস্টই ছিল। যাইহোক, সেইসময় মৈত্রেয়ী দেবী সপরিবারে কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিমা দেবী যাবেন। বরাবরের অন্তর্মুখী রথীন্দ্রনাথ ভিড় সহ্য করতে পারতেন না বলে তিনি উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে ‘পদ্মা’ বোটে গেলেন সারাদিনটা কাটাতে। সঙ্গে আবার মৈত্রেয়ী দেবী, চিত্রিতা দেবী ও তাঁদের মাসি সুব্রতা দেবীকে সারাদিনের পিকনিকের নিমন্ত্রণও জানালেন। ওদিকে প্রতিমা দেবীও মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন মৈত্রেয়ীদের। রবীন্দ্রনাথ সবদিক ভেবেচিন্তে পুত্রের নিমন্ত্রণেই যেতে বললেন। এর পরবর্তী মনোভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী বলছেন-‘অত্যন্ত পরিতাপজনক ঘটনা ঘটল, অত বড় ঐতিহাসিক মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন দেখতে পারলাম না। সারাজীবন এই নিয়ে মনস্তাপে ভুগছি। সুভাষ বোসের সঙ্গে ছবিটি যখন দেখি তখন আপসোস হয়, প্রতিমাদির পিছনে তো আমারও একটু স্থান থাকতে পারত।’

মংপুর কথায় ফেরা যাক। কবির ওই কথার সূত্র ধরেই বলি, যদিও কবি কেবলই কবিতা লেখার তুরীয়ানন্দে বিভোর হয়ে থাকেননি, সর্বদাই দেশের কথা, দশের কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন, তাও কোথাও গিয়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথও সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি চাইতেন। সেসময় মানব-সভ্যতার ইতিহাস কলুষিত হচ্ছে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের নীতিতে, চীনের ওপর সীমাহীন বর্বরতা প্রদর্শন করছে জাপান, আর কদিন পরেই বাধবে সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ। মংপুতে বসেও সেসব শুনতেন তিনি। অসহায়ভাবে বলতেন-‘ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিওর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারিনে।’
এতকিছুর মধ্যেও কাচের ঘরের জানলার কাচে ভ্রমরের ভ্রম দেখে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছেন। পরক্ষণেই ডুবে গিয়েছেন কবিতা লেখায়। মানবতার ভূলুণ্ঠন তাঁকে আহত করলেও প্রকৃতির থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি তিনি। মংপুতে তাঁকে যা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত, তা হল ফুল। বাংলোর সিঁড়িতে রাখা টবের লাল জিরেনিয়াম ফুলকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন ‘সানাই’ কাব্যগ্রন্থের ‘স্মৃতির ভূমিকা’ কবিতায়-‘বাড়ির সিঁড়ির ‘পরে/স্তরে স্তরে/বিদেশী ফুলের টব, সেথা জেরেনিয়মের গন্ধ/শ্বসিয়া নিয়েছে মোর ছন্দ।’ কবিতাটা মংপুতে বসেই লেখা। মংপুর সকালবেলার ছবি। তারিখ ৮ই জুন, ১৯৩৯।

সেবারেই এসে মনমোহন সেনের কাছে শোনেন, সেপ্টেম্বরে চেরীফুলের সমারোহ দেখা যায়। ব্যস, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন সেপ্টেম্বরে আবার আসবেন। আপনভোলা কবিটি অবশ্য সেবার কথা রেখেছিলেন। ‘কথা রেখেছিলেন’ এভাবে বলার কারণ, তাঁর ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথের মতো রবীন্দ্রনাথেরও ক্ষণে ক্ষণে মত বদলে যেত। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকেই জেনেছি, যে, ১৯৩৮ সালে শরৎকালে তাঁর আরেকবার মংপু আসার কথা ছিল। সেইজন্য মৈত্রেয়ী দেবীরা তাঁকে আনতে গিয়েওছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেই মত বদলাল, আর মংপু যেতে চাইলেন না। মৈত্রেয়ী তাই এরপর থেকে কৌশল করতেন। সরাসরি গুরুদেবকে না লিখে লিখতেন তাঁর ঘনিষ্ঠ জনদের।
যে চারবার মংপু এসেছেন, তার মধ্যে তিনবারই এসেছেন গ্রীষ্মে, আর বর্ষার শুরুতে নেমে গিয়েছেন সমতলে। কারণ, বর্ষা যতই তাঁর প্রিয় ঋতু হোক, শান্তিনিকেতনের রাঢ়ভূমির বর্ষার উচ্ছ্বলতাই তাঁকে আনন্দ দিত বেশি। পাহাড়ের স্যাঁতসেঁতে বর্ষা, শীত শীত ভাব, একঘেয়েমি খুব একটা পছন্দ ছিল না তাঁর। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন-‘মংপুতে একটানা বেশিদিন থাকবার পর যদি বর্ষা নামত তাহলে কবির সমতটে ফেরবার জন্য আগ্রহ হতো। …পরিবর্তন প্রয়াসী কবির মন পাহাড়ের বেড়া এবং আমার বেড়া সরিয়ে প্রান্তরে নেমে পড়তে চাইত। কিন্তু ফিরে গিয়েও মংপু প্রত্যাবর্তনের কথা সর্বদাই বলতেন-ছুটিগুলিতে মংপু আসবেন এ একরকম স্থিরই ছিল।’
শীতকালে মংপুর বাগানের মধু আর কমলালেবু কবিকে পাঠাতেন মৈত্রেয়ী দেবী। খুশি হয়ে উঠতেন কবি। পাঠভবনের ছাত্রদের খাওয়াতেন কমলালেবু। ‘কালিম্পং পর্বে’ বলেছি, মৈত্রেয়ীর সাথে নিয়ত খুনসুটি করতেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ সালের ৯ই জানুয়ারির চিঠিতে মৈত্রেয়ীকে লিখছেন-‘তোমার বাগানের চাকের মধু এসে পৌঁছেছে। আমার পূর্ব সঞ্চয় প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় পেয়ে খুসি হলুম। মুখে দিয়ে দেখা গেল তার মধ্যে সিনকোনার পরিচয় নেই। পুষ্প বিকাশে যেখানে গাছের কবিত্ব সেখানে বোধকরি তিক্তরসের উপদ্রব ঘটে না।’ মংপুতে যে সিঙ্কোনার চাষ হতো, তা থেকে কুইনাইন তৈরি হতো বলে এমন কৌতূক।
আরেকবার, তথ্য অনুযায়ী ১৯৪০ সালের শুরুতে, মংপুতে মধু পাওয়া যাচ্ছিল না। এর মধ্যে কবির আবদার এল পত্রকাব্যের মাধ্যমে-‘পাড়ায় কোথাও যদি কোনো মউচাকে/একটুকু বাকি থাকে,/যদি তা পাঠাতে পারো ডাকে/বিলাতী শুগার হতে পাব নিস্তার,/প্রাতরাশে মধুরিমা হবে বিস্তার।’ অবশেষে মধু পেয়ে প্রথমে লিখলেন-‘শ্যামল আরণ্য মধু বহি এল ডাকহরকরা/আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবনী বৈলাতী শর্করা/পূর্বাহ্নে পরাহ্নে মোর ভোজনের আয়োজন থেকে,/এ মধু কবির ভোগ রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে।’ তারপর আরও কিছু মধু পেয়ে লিখলেন-‘দূর হতে কয় কবি/জয় জয় মাংপবী/কমলাকানন তব না হউক শূন্য/গিরিতটে সমতটে/আজি তব যশ রটে/আশারে ছাড়ায়ে বাড়ে তব দান পুণ্য!/তোমাদের বন ময়/অফুরান যেন রয়/মৌচাক রচনায় চির নৈপুণ্য।’
রবীন্দ্রনাথকে মৈত্রেয়ী দেবী মংপুতে যেভাবে পেয়েছিলেন, তা তাঁর জীবনের চিরদুর্লভ অভিজ্ঞতা, এবং তিনি তাঁর লেখায় সে কথা স্বীকারও করেছেন অকপটে। তরুণী লেখিকার কাছে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, লেখক রবীন্দ্রনাথ, রসিক রবীন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই সাধক রবীন্দ্রনাথ ধরা দিয়েছিলেন স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে। রবীন্দ্রনাথের খুঁটিনাটি চারিত্রিক গুণ লেখিকা দেখেছিলেন স্বচক্ষে। তাঁর প্রতি সম্মানে তিনি আনত থাকতেন। কিন্তু আমাকে যেটা সবথেকে আকৃষ্ট করে বা বলা ভালো, যে কারণে মৈত্রেয়ী দেবীর উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়, সেটি হল, মৈত্রেয়ী দেবী কিন্তু তাঁর গুরুকে কখনও স্বর্গের দেবতারূপী কোনও আসনে বসাননি। যদিও এক জায়গায় লিখছেন ‘তাঁকে ডাক দিয়ে এনেছি আমার জীবন দেউলের মাঝখানে-সেখানে তিনি অদ্বিতীয় বিগ্রহ।’ কিন্তু সেটা কেবলই তাঁর সংসারের মাঝে মহামানবের উপস্থিতির দুর্লভ সৌভাগ্য স্বীকার করে নিতে। কারণ এই মৈত্রেয়ী দেবীই আবার আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন-‘রবীন্দ্রনাথ মানুষ, সর্বতোভাবেই মানুষ, আদর্শকে তিনি ভালোবাসেন কিন্তু আদর্শের সঙ্গে টানাটানিতে প্রিয়পাত্রদেরই জয় হয়ে যায়।’
এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাতনি অর্থাৎ রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা পুপে, যার ডাকনাম ছিল নন্দিনী, তাঁর বিয়েতে শান্তিনিকেতনে উৎসব হোক, এটা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবতই পছন্দ ছিল না। তাঁর যুক্তি ছিল, আশ্রমের আদর্শ এতে নষ্ট হবে। যদিও তাঁর শান্তিনিকেতনের আদর্শ বহুদিন আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবং সে কথা এই মংপুতে বসেই মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে এক সন্ধেবেলা বলেছিলেন কবি। কিন্তু তখন তিনি বৃদ্ধ, সকলের ওপর জোর খাটানোর ক্ষমতাও নেই। তাই জাঁকজমকের আয়োজন দেখে বিরক্ত হচ্ছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী বোঝাতে গেলে কবির কাছে তিরস্কৃত হন। কবির এই মনোভাব দেখে মৈত্রেয়ী দেবী বিয়েতে থাকেননি, কদিন আগে কলকাতায় চলে যান। প্রশান্ত মহলানবিশের স্ত্রী নির্মল কুমারী ওরফে রানী মহলানবিশও দক্ষিণ ভারত চলে যান। কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথই পরে বিবাহবাসরে উপস্থিত থেকেছেন, ছবি তুলেছেন, এবং মৈত্রেয়ীকে চিঠিতে লিখেছেন-‘তুমি থাকলে দেখে খুশি হতে।’ মৈত্রেয়ী দেবী এখানে সামান্য অভিমানের সুরেই বোধহয় লিখছেন-‘খুশি হবার সুযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট করেছেন নিজেই।’
মংপুতে কবি যখন থাকতেন, তখন বহু বিশিষ্ট মানুষই গিয়ে উপস্থিত হতেন। এবং যারাই আসতেন, তাঁদের ঠিকমতো যত্নআত্তি হল কিনা, সে নিয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন। প্রথমবার যখন ছিলেন, তখন হঠাৎ-আগত অতিথিদের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষের নাম পাওয়া আচ্ছে। সাঁতারু ছিলেন। বিদেশে যাওয়ার আগে কবির আশীর্বাদ নিতে অতদূর ছুটে গিয়েছিলেন। এনার কথা সত্যজিৎ রায়ের আত্মজৈবনিক বই ‘যখন ছোট ছিলাম’-এ পড়েছি। ১৯৩৪ সালে, সত্যজিৎ তখন মায়ের সাথে বকুলবাগানের মামারবাড়িতে থাকেন। ভবানীপুর সুইমিং ক্লাবে সাঁতার শিখতে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানেই প্রশিক্ষক ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষ। গায়ে শুয়োরের চর্বি মেখে নিয়ে টানা ছিয়াত্তর ঘণ্টা জলের তলায় থেকে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন প্রফুল্ল।
কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথও মংপুকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। বাবার অনুপস্থিতিতে দু-একবার সস্ত্রীক গিয়ে থেকেও গেছেন। রথীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা ছিল ঈর্ষণীয়। গাছের ফুল, পাতা চিনতেন নিখুঁতভাবে। মংপুর বনে ঘুরতে ঘুরতে বনের শোভা দেখে উল্লসিত হতেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে তাঁর পারদর্শিতার কথা তৎকালীন সময়ে খুব কম মানুষই জানতেন। বিশ্ববরেণ্য পিতার খ্যাতির ছায়ায় তিনি স্বেচ্ছায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিভার বিকাশ তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। শুধু ফুল চেনাই নয়, ফুলের ছবিও তিনি আঁকতেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর ফুলের ছবিতে মুগ্ধ থাকতেন।

বাংলোর পিছন দিকটায় একটা মরা গাছ। দেখলেই বোঝা যায়, দাঁড়িয়ে আছে অনাদিকাল ধরে। শিশির বললেন, এই গাছের নাম দিয়েছিলেন সপ্তপর্ণী। দেখলেই চেনা যায়। এ গাছ শান্তিনিকেতনের এক আইকন-স্বরূপ। ছাতিম। দ্বিতীয়বার মংপু আসার পরদিন মধুশ্রী দেবীর জন্মদিন পালন হয়েছিল এই গাছের নীচে, এ তথ্য ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’-এ রয়েছে। গাছতলার নাম দিয়েছিলেন শিলাতল। গাছটির পুরনো ছবিও দেখলাম দেওয়ালে টাঙানো। সে ছবিতেও তার পাতাঝরা কলেবর। তাই, দুটিকে পাশাপাশি মেলাতে কোনও অসুবিধা হয়নি।
এই বাংলোর পাশের পাহাড়ের গা দিয়ে একটি ঝর্ণা বয়ে যেত নীচের জঙ্গলে। রবীন্দ্রনাথকে ঝর্ণার কুলকুল ধ্বনি মুখরিত করে রাখত। প্রায়ই তিনি নানা বিষয়ে কথা বলতে গেলে ঝর্ণাটির সাবলীল গতির উপমা টানতেন। ‘সুন্দর তোমার সংসারটা ঐ ঝরনার মতো ঝর ঝর করে গান গেয়ে চলেছে’। সেই ঝর্ণা অবশ্য আজ আর নেই। কালের নিয়মে প্রকৃতির আজব খেয়ালে সে শুকিয়ে গেছে তার সোনালী ইতিহাস-কাকলিকে সঙ্গে নিয়েই। মৈত্রেয়ী ও মনোমোহনের পুত্র প্রিয়দর্শী সেন একবার লিখেছিলেন-‘একটি ছোট্ট দুরন্ত ঝরনা পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আমাদের বাগানের ভিতর দিয়ে নাচতে নাচতে নিচের বস্তি হয়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকাত। অনেক কথা বলতে বলতে সে যেত কিন্তু তার ভাষা বোঝার আশা সবাইকেই জলাঞ্জলি দিতে হতো। বাড়ির এই ঝরনাটির অক্লান্ত কলধ্বনি বাগানটাকে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে প্রানবন্ত করে রাখত। ক্রমে এই ঝরনাটি হারিয়ে যায়-তার স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ, তার অক্লান্ত গান আজ আর নেই। পৃথিবীর বিশাল বিপুল ইতিহাসের পাতা থেকে ওই ক্ষনিকের অতিথি ঝরনা ঝরে গেছে। এতো গেল বাংলো বাড়ির বাইরের কথা, আর ঐ ছোট্ট বাড়ির ভিতরে আর এক ক্ষনিকের অতিথি আমাদের অতি শ্রদ্ধার ও সম্মানের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঝর্নার কলধ্বনির মতো হাসি, গান, ছবি ও কবিতা দিয়ে তাঁর উপস্থিতির আশীষ দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই উপস্থিতির অনুরণন অনেকদিন ঐ বাড়িকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল।’
মংপুতে এসে কবি আরেকটি পাগলামি করেছিলেন। তৃতীয়বার মংপু থেকে ফেরবার সময় ডক্টর সেনকে বাংলোর চত্বরে মাঠের মাঝখানে গাছের ডাল দিয়ে একখানা ঘর বানাতে বলেছিলেন। পরের বার এসে সেটার খোঁজ করেন। বানানো হয়েছে জানতে পেরে সেখানে একবেলা ছিলেনও। ঘরটার নাম দিয়েছিলেন ‘শৈল কুলায়’। এই ঘরটিও দেখতে পাইনি। তবে পরে প্রিয়দর্শী বাবুর কাছে শুনেছি, সেই ঘরটা আরও অনেকদিন ছিল, তিনিও ছোটবেলায় দেখেছেন। কিন্তু পরে কালের নিয়মে সেও ভাঙা পড়েছে। মূল বাংলো থেকে খানিক দূরেই ছিল ঘরটা। তবে সেটা রবীন্দ্রনাথ বানাতে বলেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে প্রিয়দর্শী বাবু সন্দিহান।
আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই পরিচ্ছেদের যবনিকা টানব। রেলপথ নিয়ে আমার আগ্রহের কথা কালিম্পং পর্বে বলেছি। সেখানে গেলিখোলা স্টেশনের কথা বলতে গিয়ে তিস্তা ভ্যালি রেলওয়ে এক্সটেনশনের কথাও বলেছি। প্রবোধ সান্যালের লেখায় সে রেলপথের বর্ণনা ছিল। এই রেলপথেরই রিয়াং স্টেশনে নেমে আসতে হতো মংপু। যাওয়ার জন্য। ছোট্ট পাহাড়ি স্টেশন। সেখানের ব্যবস্থাও সামান্য। তবে সেখানে সাহেবি কূপ ছিল, যা দেখে মনে হতো অতীব সুন্দরী রাজকন্যা যেন বসে আছে। এই প্রসঙ্গে অমিয় বসুর ‘বাংলায় ভ্রমণ’-এর প্রথম খণ্ড থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না – ‘কালীঝোরার পর রিয়াং স্টেশন পেছিবার পূর্বেই তুষারাবৃত পৰ্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াং নদীর পুল পার হইয়া রেলপথ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কৌশলে পুলের উপরে রিয়াং স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। রিয়াং শিলিগুড়ি হইতে ২৫ মাইল। কয়েক বৎসর পূর্বে রিয়াং নদী এক রাত্রির মধ্যে পুরাতন খাদ ত্যাগ করিয়া নূতন খাদে বহিতে থাকে। পুরাতন পুলের স্তম্ভগুলি শুষ্ক পাথর ও মুড়ির মাঝে দাড়াইয় পুৰ্ব্বকার খাদের সাক্ষ্য দিতেছে।
রিয়াং স্টেশন হইতে মাত্র ৩৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রিয়াং নদীর উত্তরে অবস্থিত মংপু গ্রাম। দাৰ্জিলিং পথের সোনাদা স্টেশন হইতেও মংপু যাওয়া যায়; সোনাদ হইতে পূৰ্ব্বদিকে ১১ মাইল দূর এবং মাঝপথে ৫,৬১৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত সরাইল বাংলা পড়ে। মংপু বঙ্গের সিনকোনা আবাদের সদর ও প্রধান কেন্দ্র, এই অঞ্চল সিনকোনা চাষের বিশেষ উপযোগী।’
দ্বিতীয়বার মংপু থেকে ফেরবার পথে রবীন্দ্রনাথেরই জোরাজুরিতে সেন পরিবারও তাঁদের সকলের সাথে শিলিগুড়ি এসেছিলেন তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে। দিনটি ছিল ১৭ই জুন, ১৯৩৯। সেইদিনটি পাহাড়ি ছোট্ট স্টেশনটার ওই গুটিকয়েক মানুষ, যাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় কখনও স্থান পায়নি, তাঁদের জন্য কতখানি স্মরণীয় ছিল তাই ভাবি। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকেই বলি-‘ট্রেন আসতে তখনও কিছুক্ষণ দেরি ছিল, কোনো রকমে একটা ভদ্রগোছের হাতাওয়ালা চৌকি যোগাড় করে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের উপর ওঁকে বসানো হল। সামনে প্রকাণ্ড উদ্ধত পাহাড় গভীর অরণ্য বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে, নীচে স্রোতস্বিনী কলভাষিণী নদী, মাঝখানে বসে আছেন জগতের মহাকবি, মহিমান্বিত স্তব্ধ সমাহিত মূর্তি।’
মংপু যেমন রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, রবীন্দ্রনাথও বুঝি মুগ্ধ করেছিলেন মংপুকে।
৪
মংপু-রবীন্দ্রনাথ-বিশ্ব
“এ নির্জন অরণ্যে বিশ্বকবির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বও এল, আমি পৃথিবীর মানুষের সঙ্গ পেলাম। দেশবিদেশের গল্প শুনতাম। বার্গসঁ, যাঁর দর্শন পড়েছি যিনি একজন জীবিত মানুষ তা ভাবি নি কখনো-তাঁর কথা শুনলাম। বার্নার্ড শ’, রোমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল সব বইয়ের মলাটের নামগুলো নানা কথা বলতে লাগল। অজ্ঞাত বিশ্বের দৃশ্য দেখলাম।”
উপরের কথাগুলি মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর অতিবিখ্যাত আত্মজৈবনিক উপন্যাস ‘ন হন্যতে’তে বলিয়েছিলেন অমৃতার মুখ দিয়ে। সচেতন পাঠক মাত্রেই জানেন, উপন্যাসের অমৃতার সত্তা আর বাস্তবের মৈত্রেয়ীর সত্তায় কোনও প্রভেদ নেই। সদ্যযৌবনা মংপুবাসিনী মৈত্রেয়ী দেবী যখন নির্জন পার্বত্য অরণ্যে চরম একাকীত্বে ডুবে গিয়েছিলেন, সেসময় তাঁকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছিল কবির এই বারবার আগমন। সেই একাকীত্বের বর্ণনা এই উপন্যাসে ছিল। আর তিরিশের দশকের শেষভাগে হাঁসফাঁস করতে থাকা মানব-সভ্যতার পট-পরিবর্তনের আঁচ থেকে দুর্গম মংপুও যে বাঁচতে পারেনি, এ কথাও সেই উপন্যাসে ছিল।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে মংপু গিয়েছেন, সেসময়ে বিশ্ব-ইতিহাসে মানবতার যেরকম ভূলুণ্ঠন হয়েছে, তেমনটা বোধহয় আর কখনও ঘটেনি। জার্মানি আর ইতালির ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন তো ছিলই, এবং সেই আগ্রাসনকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করার কোনও চেষ্টাই করেনি সর্বশক্তিমান ব্রিটেন। এর সঙ্গে সেইসময় চীনে সংঘটিত হচ্ছে জাপানি বর্বরতার নামান্তর। স্পেনে প্রজাতন্ত্রবাদী কমিউনিস্ট আর একনায়কতন্ত্রবাদী ন্যাশনালিস্টদের মধ্যে চলছে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। তাই মংপুতে তিনি যা আলোচনা করতেন বা লিখতেন সেখানে বারেবারেই মানব সভ্যতার এই অসহনীয় রূপের কথা এসে পড়েছে। মানুষের কথা বলতে গিয়ে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারেননি, আবার এর উল্টোটাও তাঁর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।
“মনে পড়ে প্রত্যেকদিন রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে, মানুষের এই হিংস্রতার কলঙ্কে কী বেদনা তিনি পেতেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি সাধনা করেছেন মানুষকে মানুষের নিকটে আনতে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির আদর্শকে তিনি ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে একত্র করতে চেয়েছেন-নিত্য উৎসারিত প্রেমের, আনন্দের বাণী তিনি শুনিয়েছেন সমস্ত জগৎকে,-কোথায় প্রেম, কোথায় আনন্দ, কোথায় মানুষের মনুষ্যত্ব, সমস্ত জগৎ যখন এমন পাগল হয়ে বিকৃত বুদ্ধিতে এঁকে আর একের গলা চেপে ধরল তখন দেখেছি তাঁর বেদনা।–আমাদের কাছে দূর দেশের যুদ্ধ অনেকটা পরিমাণেই যুদ্ধের গল্প ছিল, কিন্তু সকল দেশ সকল মানুষ যাঁর কাছে আপন, তাঁর কাছে আর্ত মানুষের দুঃখ প্রতিদিন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে পৌঁছত।”
উদ্ধৃতিটির শুরু থেকে মোটামুটি আমাদের চেনা কথা। শেষবয়সে উপনীত হয়ে মানব-দরদী কবি মানবতার ভূলুণ্ঠন দেখে বুকের মধ্যে তীব্র বেদনা অনুভব করছেন, এ কথা বহুবারই বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বোধহয় শেষোক্ত কথাটি। আমাদের মতো সাধারণ, দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া মানুষের কাছে সত্যিকারেই অন্য দেশের যুদ্ধের গল্প তেমন উদ্বেগ জাগায় না। তা নিছকই গল্প হয়ে থাকে। যেটুকু বেদনার উদ্ভব হয়, তা ক্ষণিকের। যতক্ষণ না সেই আঘাত আমাদের নিজেদের জীবনের উপর প্রত্যক্ষ ভাবে এসে পড়ছে, ততক্ষণ সেই আঘাতের অভিঘাত সম্যকভাবে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সত্যিই সম্ভব হয় না। আর এইখানেই রবীন্দ্রনাথ দোষগুণ-সম্পন্ন মানুষ হয়েও আমাদেরকে ছাপিয়ে যান। এভাবেই বুঝি নর থেকে নরোত্তমে উত্তরণ।

চীন ও জাপান দুইই তাঁর অতি প্রিয় দেশ ছিল। দুটি দেশেই তিনি প্রভূত সম্মান পেয়েছিলেন। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যেকার এমন হানাহানির চিত্র তাঁকে অস্থির করে তুলত। সাধারণ চীনা মানুষের উপর জাপানের সীমাহীন বর্বরতার ছবি তখন প্রকাশিত হয়েছে সারা বিশ্বে। সে দৃশ্য তাঁকে কি পরিমাণ কষ্ট দিত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়বার যখন মংপুতে ছিলেন, তখন পুরোদমে চলছে জাপানী আগ্রাসন। বিলাপ করতেন-“চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হয়ে উঠল। আশ্চর্য এই, যত দুঃখ পাও, যতই শুভ ইচ্ছা করো, এতটুকুও শুভ ঘটাতে পারো না,-শুভ কামনার, কল্যাণ বুদ্ধির কোনো ফলই নেই। বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। মানুষ মানুষের বুকে অকারণ বার বার নিষ্ঠুর ছুরি উদ্যত করছে, এ নৃশংসতা আর কত দেখব।”

সংবাদপত্রে প্রকাশিত জাপানি বর্বরতার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যাক, এবং তা পড়ে কবির কী অবস্থা হয়েছিল সেটাও বলা এখানে অত্যুক্তি হবে না। খবরটি ছিল এইরকম-এক চীনা কৃষকের ঘরে ঢুকে স্বামীকে বন্দি করে তার চোখের সামনেই তার স্ত্রীকে চরম লাঞ্ছিত করেছে জাপানি সেনা ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে তাদের একমাত্র শিশুটিকে। মংপুতে তখন খবরের কাগজ আসত বিকালবেলা। খবরটা পড়ে সেদিন সারা সন্ধে নীরব ছিলেন কবি। একটিও কথা বলতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, তাঁর মধ্যে একটা ‘বড় আমি’ ও আরেকটি ‘ছোট আমি’ সর্বদাই বর্তমান। চরম দুঃখের সময়ে তাঁর অস্বাভাবিক শান্ত মূর্তি আসলে তাঁর ‘বড় আমি’র প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াত। একই কথা লিখেছেন এইসব ঘটনার শ্রোতা ও প্রধান সাক্ষী, এই লেখার কেন্দ্রীয় চরিত্র মৈত্রেয়ী দেবীও-‘জীবনে কত ছোট ছোট ঘটনায় কবির এই সত্য সাধনার অন্তররূপ বাহিরে প্রতিবিম্বিত হত তার কতটুকুই বা লক্ষ্য করবার শক্তি এবং সুযোগ আমাদের হাতে ছিল? তবে সেদিন এই চীনা পরিবারের দুঃখের বেদনা যখন আত্মীয় বিয়োগের মতই আঘাত হানতে দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল এ সেই “বড় আমি”র রূপ এ সেই বিশ্বসত্তা এ সেই অন্তসীমায় আবির্ভূত অনন্ত। অথচ ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট কখনো অতিকায় হয়ে উঠত না। ব্যক্তিগত শোকে তিনি অধৈর্য্য হতেন না। কারণ দূরের মধ্যে পরের মধ্যে প্রসারিত তাঁর চৈতন্যে ব্যক্তিগত দুঃখের ভার হাল্কা হয়ে যেত। তাকে প্রাধান্য দিতে কখনই চাইতেন না। “বিশ্বজগত আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?”’

জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির সাথে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ বিতর্কে এইসময়ে পত্রে তাঁর রীতিমত বাগযুদ্ধ হয়েছে। জাপানের চীন আক্রমণকে নোগুচি আড়াল করতে চেয়েছিলেন এই বলে যে, চিয়াং কাইশেকের সরকার দেশকে পশ্চিমী সভ্যতার কাছে বেচে দিয়ে নিজেরা পশ্চিমের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে; তাই এশিয় সংস্কৃতিকে বাঁচাতে যুদ্ধ অবধারিতই ছিল। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের কলম বিদ্ধ করেছে জাপানী অন্ধ-জাতীয়তাবাদকে। নোগুচিকে তিনি লিখেছিলেন-‘Humanity, in spite of its many failures, has believed in a fundamental moral structure of society. When you speak, therefore, of ‘the inevitable means, terrible though it is, for establishing a great new world in the Asiatic continent’—signifying, I suppose, the bombing of Chinese women and children and the desecration of ancient temples and universities as a means of saving China for Asia— you are ascribing to humanity a way of life which is not inevitable even among the animals and would certainly not apply to the East, in spite of her occasional aberrations. You are building your conception of an Asia raised on a tower of skulls.’

এর আগে ‘কালিম্পং পর্বে’ এ কথা উল্লেখ করেছিলাম, যে, ১৯৩৭-এর শেষের দিকে কবির শরীরের উপর যে ইরিসিপ্লাস রোগের আক্রমণ হয়েছিল, সেইসময়ে কবিকে চীন থেকে কবিকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন ড. সাই ইয়ান-পেই ও দাই জিতাও। নিজদেশের চরম দুর্দশার পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁরা যে বিদেশী কবির স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাঁকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাতে কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন কবি।
সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘটে চলা নতুন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার কথা মৈত্রেয়ী দেবী শুনতেন কবির কাছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েতের অগ্রসর নিয়ে কবির উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেত। আগ্রহের সাথে পড়তেন ‘দ্য মস্কো নিউজ’। মস্কো নিউজ তখন সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত হওয়া একমাত্র ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র। তবে একই সময়ে স্ট্যালিনের সোভিয়েতে লৌহযবনিকার আড়ালে যে পৈশাচিক অত্যাচার ঘটেছিল, নিশ্চিতভাবেই সেই অধ্যায় সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মতো রবীন্দ্রনাথও সেই সময়ে অবগত ছিলেন না। ব্রিটিশ-বিরোধী সোভিয়েতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। সে কারণেই মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে যখন জার্মান আক্রমণ চলছে রাশিয়ার উপর, তখন রাশিয়া কোণঠাসা, তারমধ্যেও সামান্য প্রতিরোধের খবর পান অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের মুখে। তা শুনে আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন-“পারবে, পারবে, ওরাই পারবে। ভারি অহঙ্কার হয়েছে হিটলারের।” তাঁর এমন সোভিয়েত-প্রীতি ‘দ্য গ্রেট পার্জে’র কথা জানা থাকলে কতটা অক্ষুণ্ণ থাকত তা নিয়ে সন্দেহ আছে।
কেবল মানুষে-মানুষে হানাহানিই যে তাঁকে দুঃখ দিয়েছে এমনটা নয়, তাঁকে সবচেয়ে বেশি বিঁধত তাঁর নিজের অক্ষমতা। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এ কথা ভাবলে, যে, জিউস তো তাঁকে দিয়ে যাননি পৃথিবীর দায়িত্ব, তাহলে এত কষ্ট তিনি কেন পাচ্ছেন! আসলে, সারাজীবন দেশে-বিদেশে আনন্দের বাণী প্রচার করে আসা লোকটা ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন। শেষদিন অবধি বলে গিয়েছিলেন ‘মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ’, সে বিশ্বাস তিনি হারাননি, নয়ত সভ্যতার সংকটে ইংরেজ জাতির সর্বগ্রাসী দর্পের নিন্দা করতে গিয়ে একইসঙ্গে মহানুভব অ্যান্ড্রুজের কথাও তিনি উচ্চারণ করতেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত মত, নিজের জীবনভর আদর্শের প্রতি হয়ত তিনি সামান্য হলেও বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।
যে কবি ‘মৃত্যুঞ্জয়’ লিখেছিলেন, তিনিই মৈত্রেয়ী দেবীর ‘কেমন আছেন?’ প্রশ্নের উত্তরে বলে যাচ্ছেন অনর্গল-‘বেঁচে আছি এইটাই দুঃখ। …এই যে দেশের উপর হানাহানি চলেছে, ওরা তো অপরিচিত নয়, ওখানে কত সুন্দর দিন কত আনন্দে কাটিয়েছি। মনে পড়ে সেই সব হাসি হাসি মুখ, আদর অভ্যর্থনা, আর কষ্ট হয়,-কেন এ অত্যাচার, এ কি এ। জগৎব্যাপী আজ যে হানাহানি, যে বিরাট মরণযজ্ঞের আয়োজন চলেছে, সেই ভীষণ দুঃখের সামনে নিজেদের ছোট খাট সুখদুঃখগুলো এত তুচ্ছ এত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় যে, তাদের আর কোনো প্রাধান্য দিতেই লজ্জা পাই। অথচ যত বেদনাই লাগুক একটা কড়ে আঙুল তুলেও তো সাহায্য করতে পারব না কাউকে, তবে নীরব বেদনার কোনো কি মূল্য নেই? কি জানি! যেমন মানুষের হাতে শাণিত ছুরি, মানুষের হিংস্র আক্রোশ লেলিহান হয়ে উঠেছে, একি একেবারে নিষ্ফল নিরর্থক হবে?’

অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী ছিলেন একজন ড্যানিশ মহিলা। নাম ছিল হিয়োর্ডিস সিগার্ড। ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে দুজনের বিয়ে হয়। হিয়োর্ডিসের তরফে কন্যাকর্তা ছিলেন অ্যান্ড্রুজ। বিয়ের পরে কবি তাঁর নাম দেন হৈমন্তী। চতুর্থবার মংপুতে তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীও ছিলেন। ডেনমার্কে যখন গিয়েছিলেন তিনি, তাঁর সম্মানে সারারাত ধরে সেখানে আলোর উৎসব হয়েছিল। যুদ্ধের কথা বলতে বলতে তাঁর কেবলই মনে পড়ত সেসব কথা, একই কথা বারবার বলতেন। অমিয় চক্রবর্তীকে দেখেই বলতে শুরু করেন-‘এই তো তোমার শ্বশুর বাড়ি ডেনমার্ক গেল, কী সুন্দর দেশ। আর মনে পড়ে সেই তাদের টর্চ লাইট প্রসেশন, সারারাত্রি ধরে কী উৎসবই করেছিল তারা। অথচ আমি তাদের কে, কতটুকু বা তারা আমার পরিচয় পেয়েছে, কিই বা তাদের আমি দিয়েছি। এতটুকু এতটুকু অনুবাদ হয়েছে আমার বই এর, তাই দিয়েই তো আমার পরিচয় পেয়েছে? সে কতটুকু? অথচ কী অজস্র অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমায় উপহার দিয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি কি করে এ সম্ভব হল।’

এক পরাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে তিনি পাশ্চাত্যে যে বিরল, অপ্রত্যাশিত সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন, তা তাঁকেও অবাক করে দিয়েছিল। হাঙ্গেরিতে তাঁকে দেখতেই শুধু বহু মানুষ ভিড় করেছিল। এ কথা সত্যি, যে, তিনি নিজের কর্মসমুদ্রের মহিমায় যেমন সম্মান আদায় করেছে, আবার তিনি যে প্রাচ্যের মানুষ হয়েও এমন সৃষ্টিরসের অধিকারী হতে পারেন, সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য মানুষ সেই অপার বিস্ময় থেকেও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু যাই হয়ে থাকুক, সম্মান তো আর মিথ্যে নয়। ‘কালিম্পং পর্বে’ই প্যারিস পতনের দিন বেতারে ‘ডাকঘর’ অভিনয়ের আশ্চর্য সমাপতনের কথা লিখেছিলাম। রাশিয়ার দুর্দিনে ‘রাজা’ নাটকের বারবার অভিনয়ও তাঁর মনে পড়েছিল সেদিন। এমন সম্মান তিনি যাদের কাছ থেকে পেয়েছেন, তাদেরকেই এরকম হত্যালীলায় মত্ত হতে দেখলে কী হতে পারে তাঁর মনের অবস্থা এ বুঝি এত বছর পরেও আজকের মানুষের অবোধ্য হবে না।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি মহাভারতের কথা বলতেন। বাস্তব যুদ্ধের পটভূমিকায় তিনি মহাভারতের যুদ্ধকে দেখেছিলেন। পৃথিবীর প্রতিটি মহাকাব্যের আখ্যানেই যে যুদ্ধকে মহিমান্বিত করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর কটাক্ষপাত ছিল। কিন্তু তিনি মনে করতেন, মহাকাব্যে যুদ্ধের বর্ণনাটাই আসল নয়। তার প্রকৃত নির্যাস লুকিয়ে আছে অন্যখানে। সেই কারণেই মহাভারতের অন্তে যুদ্ধবিজয়ের পর পাণ্ডবদের পৈশাচিক বিজয়োল্লাস যে দেখানো হয়নি, বরং দেখানো হয়েছিল, যে তাঁরা সকলে শান্তিলোক অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেইটিই যে এই মহাকাব্যের মূল সুর, সে কথাই বারবার বলতেন রবীন্দ্রনাথ।
তাঁর জীবনের এই পর্বটা যতবারই আমি পড়ি, ততবারই আমার কেবল একটাই কথা মনে হয়। শ্রুতিকটূ মনে হতে পারে। তবে একথাই আমার মনে হয়, ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট অনন্তলোকের পথে যে যাত্রা করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী কবি, তা তাঁর পক্ষে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছিল। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস যেদিন পড়েছে, সেদিনের পর থেকে যত সময় এগিয়েছে, তত আরও নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর নখদন্ত প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা দেখেছে ‘উন্মত্ত পৃথ্বী’। বিয়াল্লিশের দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিরোশিমা-নাগাসাকি, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, রক্তাক্ত স্বাধীনতা, দেশভাগ-একের পর এক।
বেঁচে থাকলে বিশ্বকবির বিলাপধ্বনি সেদিন হয়ত শুনতে পেত না বিশ্ব।




