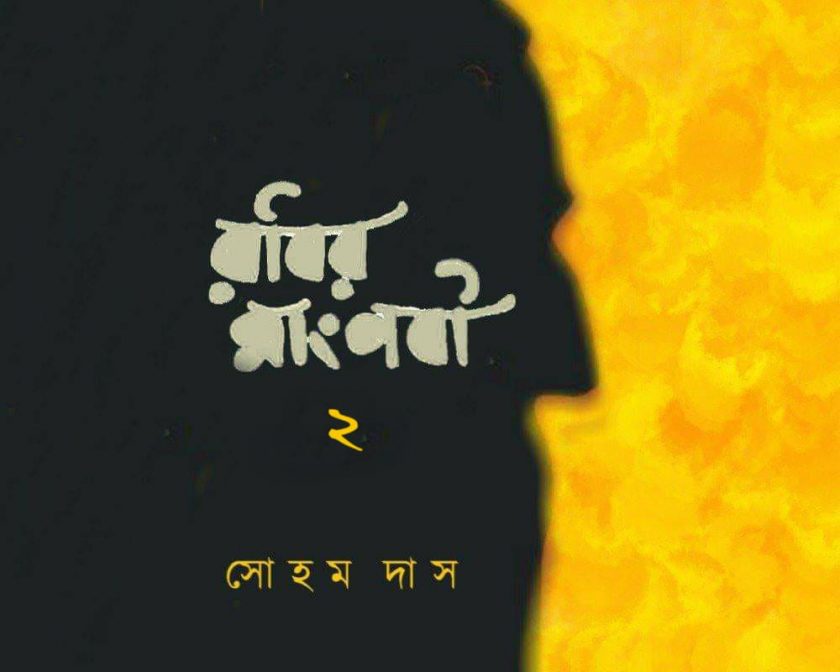
৩.
মৃত্যুশ্রান্ত কবি
ঐতিহাসিক রেডিও-অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরই ২১শে মে কবি শেষপর্যন্ত মৈত্রেয়ীর আবদার রক্ষা করে মংপুতে গিয়েছিলেন। এরপর আরও তিনবার তিনি মংপু এসেছেন। কোনওবার শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি, কখনও বা কালিম্পং হয়ে। শেষবার যখন মংপু এলেন ১৯৪০ সালে, সেবার আগে কালিম্পং এসেছিলেন। তারপর একদিন পরেই মংপু যান। কিছুদিন মংপুতে কাটিয়ে আবার কালিম্পঙে ফেরেন। কালিম্পঙে পৌনে দু’মাস কাটিয়েছিলেন (৭ই মে থেকে ২৯শে জুন)। সেবারের পর্বতবাসের অধ্যায়টি জুড়ে কেবলই প্রিয়জনের মৃত্যুযন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন চির-আনন্দময় কবি।

কালিম্পং যাওয়ার কয়েকদিন আগেই মারা গেলেন চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজ। কবির কর্মজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহকর্মী। ১৯৪০-এর শুরুতেই কলকাতায় এসে গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন। ২৭শে জানুয়ারি নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন। দু’মাসের কিছু বেশিদিন হাসপাতালের বিছানায় কাটিয়ে ৫ই এপ্রিল অন্তিমলোকে যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ‘চার্লি’। এই চার্লি যিনি কিনা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন, অথচ, গুরুদেবের সংস্পর্শ পেয়ে যাজকের কাজ চিরতরে ত্যাগ করে হয়ে উঠলেন মানুষের প্রকৃত বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজির মধ্যে মিলনের সেতুটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে যিনি রচনা করেছিলেন, সেই মানুষটিও হলেন এই চার্লি। তাঁকে এই সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন স্বয়ং ‘বড়দাদা’ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন হবে নাকি সুপ্রাপিউবিক ক্যাথিটার পরানো হবে সেই নিয়ে আলোচনা চলছিল। মহাত্মাজি নিজে এসে বললেন-বুকে বল আনো, চার্লি। মোহনকে (অর্থাৎ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী; অ্যান্ড্রুজই বোধহয় ইতিহাসে পরিচিত একমাত্র ব্যক্তি, যিনি গান্ধীজীকে অবলীলায় তাঁর ফার্স্ট নেম ধরে সম্বোধন করতেন, এমনই ছিল তাঁদের বন্ধুত্বের শিকড়) বিশ্বাস করেই বুঝি রাজি হলেন। কিন্তু অপারেশনের ধকলটা শেষপর্যন্ত নিতে পারলেন না কর্মোদ্যমী মানুষটি।
জীবনের অন্তিমপর্বে এসে কবি হারালেন তাঁর বড় ভালোবাসার জনটিকে। সেই ১৯১২ সালে লন্ডনের হ্যামস্টেড হীথে চিত্রকর উইলিয়াম রথেনস্টাইনের বাড়িতে দেখা হয়েছিল দুজনের। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির অনুবাদ-পাঠ। রবীন্দ্রনাথের সাথে ইংরেজ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস। তারপর দীর্ঘ আঠাশ বছর তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন ওতপ্রোতভাবে। অ্যানড্রুজ তাঁর ‘What I owe to Christ’-এ লিখে গিয়েছেন কীভাবে গুরুদেবের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজে কোনোরকম বাধা দেননি। সেসময় চার্লস বর্ধমানের গির্জায় যাজক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এমন সময়ে ট্রিনিটি সানডের (ইস্টারের পর অষ্টম রবিবার) দিন আথানাসিয়ান ক্রিড পাঠ করে তাঁর নিজেরই মনে হল, এ তিনি কী করছেন! শান্তিনিকেতনের স্থানীয় মানুষদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা জন্মেছে, তার সাথে এই পাঠ তো যায় না। ছুটলেন কবির কাছে। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়-
‘শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর যখন কবির মুখচ্ছবি দেখলাম তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন তখনই আমি বুঝলাম যে আমি অসত্য পথে চলেছি এবং এখনই আমাকে এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে। …আমি তাঁর পবিত্র আত্মার সামনে দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাই যা যা ঘটেছিল সমস্তই তাঁর কাছে স্বীকার করলাম এবং সেইদিন থেকেই আমি কি করব, কেমন করে সত্যকে পাব তা স্থির করলাম। কবি বিচলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন তাড়াতাড়ি কিচ্ছু না করতে কিন্তু যে মিথ্যার খাদের ধারে আমি দাঁড়িয়ে আছি তখন তা আমি বুঝতে পেরেছি। …দুটি চিঠি সেই দিনই আমাকে লিখতে হলো। লেখা কঠিন ছিল, একটি বিশপকে, তাঁকে জানাতে যে কি কারণে আমি বর্ধমানের চার্চে আর রবিবারে প্রার্থনা করতে পারব না। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখতে হলো আমার বাবাকে। সেদিন থেকে আমি আর কখনো যাজকের কর্ম করিনি।’
মৈত্রেয়ী দেবী অ্যানড্রুজকে নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন একটি মজার ঘটনা। একদিন তিনি আর রথীন্দ্রনাথ গাড়িতে করে চলেছেন শ্রীনিকেতনের উদ্দেশ্যে। তখন ভরা গ্রীষ্ম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখেন কিনা, ঝাঁ-ঝাঁ রোদে খালি মাথায় খালি পায়ে বীরভূমের খরতপ্ত লালমাটির ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে চলেছেন ধুতি-পরিহিত ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ অ্যানড্রুজ সাহেব। দুজনে শত অনুনয় করেও কোনও ফল হল না। অ্যানড্রুজের জেদের কাছে দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে হার মানলেন। রোজ সকালে চার্লি কবিকে সুপ্রভাত জানাতেন ‘গুরুদেব’ বলে গলা জড়িয়ে ধরে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন বাদে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে মংপুতে বসে মৈত্রেয়ী-বর্ণিত সেই দৃশ্যটির কথাই যেন বলেছিলেন-“কেবল মনে পড়ে সেই লাল ধূসর জামা কাপড়, ধুতি খুলে খুলে পড়ছে, কোনোমতে সামলে চলেছে সন্ন্যাসী।”

যাইহোক, আমরা আবার ফিরে যাই উপরিউল্লিখিত সময়ে। অ্যানড্রুজ মারা গেলেন ৫ই এপ্রিল। তার ন’দিন বাদে নববর্ষের দিন রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালিত হল। সুদূর চীন থেকে সর্বময় নেতা মার্শাল চিয়াং কাই-শেক এবং শিক্ষামন্ত্রী চিয়েন লি-ফু জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠালেন। কবি এরপর কালিম্পং যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। ১৭ই এপ্রিল কলকাতায় এসে ১৯ তারিখ বরিশালের কাঠের ব্যবসায়ী যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা বিল্ডার্স স্টোর্স লিমিটেডের ট্রাস্ট হাউস উদ্বোধন করলেন। সেইদিনই মে-ফেয়ারে গিয়ে দেখে এলেন মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর বড় আদরের ভাইপো সুরেনকে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ)। সেই চোদ্দ বছর বয়সে মাকে হারানো দিয়ে শুরু, আশির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও আপনজনের মৃত্যুবেদনা তাঁকে ছাড়ল না। রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন-‘বুঝতে পারচি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে সুরেন পেরে উঠবে না। এত কষ্টও পাচ্ছে। নানা রকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনটা গেল। অমন মানুষের ভাগ্যে এত কষ্ট ঘটতে পারে এ কথা ভাবলে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপর। মনের ভিতর বৃথা ছটফট করতে থাকে।’
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন নব্বই পার করেছেন। লুপ্তস্মৃতি। রবি তাঁকে প্রণাম করে বলেন-‘আমি রবি।’ প্রিয় দেওরকে চিনতে পারেননি এককালের সেই সাহসিনী যুবতীটি। একথা মৈত্রেয়ীকে বলতে গিয়ে কবির পার্সোনাল সেক্রেটারি সুধাকান্ত রায়চৌধুরি আরও বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রণম্য কেউ আছেন দেখলে বেশ মজা হয়। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হল মংপু থাকাকালীনই। ৫ই মে, ১৯৪০। বাংলা ২২শে বৈশাখ, ১৩৪৭। মংপুতে কবির জন্মদিন পালন হচ্ছে সেদিন। স্থানীয় নেপালী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে সে এক ভিন্ন স্বাদের জন্মদিন পালন। পরদিন সুধাকান্তবাবুর মুখে শুনলেন প্রত্যাশিত দুঃসংবাদ। সেইদিন সন্ধেবেলায় অসীম শূন্যের পানে চেয়ে শুধু বলেছিলেন-‘কেউ জানল না সে কী আশ্চর্য মানুষ ছিল। এমন মহৎ, এমন একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ সকলের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, অগোচরেই চলে গেল, যারা জানে শুধু তারাই বুঝবে-এমন হয় না, এমন দেখা যায় না।’ চিরন্তন শোকের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী কবির বিলাপ কেবল এইটুকুই!
‘স্বর্গের কাছাকাছি’তে মৈত্রেয়ী দেবী জানাচ্ছেন, তৃতীয়বার মংপুতে এসে সেখানে বসেই সুরেন ঠাকুরের ‘বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ’ পড়েছিলেন কবি। তাঁর ভয় হয়েছিল, সুরেনের ওপর হয়ত ব্রিটিশ সরকারের করালদৃষ্টি পড়তে পারে। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর একবছরের ছোট বোন ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে ইংরেজি শেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ দারুণ সাহায্য পেয়েছিলেন। বিশেষত, worm আর warm এর ভিন্ন উচ্চারণ এই দুই ভাইবোনই তাঁকে শিখিয়েছিলেন। মংপু থেকেই ইন্দিরাকে লেখা চিঠিতে সেই দুঃখ ঝরে পড়ছে-‘তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসে ছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধ ভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয়নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আসব, সেইদিন নিকটে এসেছে।’
পরদিন ৭ই মে কবি কালিম্পং চলে এলেন। রথীন্দ্র-প্রতিমা তখন কালিম্পঙে এসেছেন। মংপুতে আবারও ফেরবার কথা ছিল দিন সাতেকের মধ্যেই, সেকারণে বেশ কিছু গরম জামাকাপড় আর ব্যবহার্য সামগ্রী রেখেও এসেছিলেন মৈত্রেয়ীর হেফাজতে, কিন্তু আর যাওয়া হয়নি কোনও কারণে। পাঁচদিনের মাথায় এল তৃতীয় মৃত্যুসংবাদ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পথচলার একদম প্রথম যুগ থেকে যিনি কবির পাশে ছিলেন, কর্মে ও নিষ্ঠায়, সেই কালীমোহন ঘোষ আর নেই। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে বিশ্বভারতী হারাল তাদের অন্যতম দুই কর্মনিষ্ঠ বন্ধুকে।

রবীন্দ্রনাথের ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধ পড়ে স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে ত্রিপুরা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে এসেছিলেন বাইশ বছরের মেধাবী তরুণটি। সেটা ১৯০৬। তারপর আমৃত্যু জড়িয়ে ছিলেন আশ্রমের সাথে। কবিগুরুর নির্দেশে ও ইচ্ছায় ইংল্যান্ড থেকে শিখে এসেছিলেন প্রাথমিক ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাদানের পদ্ধতি। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে যখন শ্রীনিকেতনে ইনস্টিটিউট অফ রুরাল রিকনস্ট্রাকশন স্থাপিত হয়, সেই কাজে লিওনার্ড এল্মহার্স্টের প্রধান সহকারী হয়ে উঠেছিলেন কালীমোহন। বিলেতে শিখে আসা বিদ্যের যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছিল।
শ্রীনিকেতনের কথা যখন উঠলই, তখন লিওনার্ড এল্মহার্স্টের কথাও এখানে অল্প করে বলা দরকার। ১৯২১ সালের মার্কিন সফরে রবীন্দ্রনাথের সাথে এল্মহার্স্টের দেখা হয়েছিল। এল্মহার্স্ট তখন নিউইয়র্কের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ইয়ং মেন’স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে ভারতের গ্রামাঞ্চলে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। কবির সাথে দেখা হলে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৫ এই তিনবছরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তাকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তোলার ক্ষেত্রে যেদুটি মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন এই কালীমোহন ঘোষ ও লিওনার্ড এল্মহার্স্ট। এল্মহার্স্টের স্ত্রী মার্কিন সমাজকর্মী ডরোথি পেইন হুইটনি স্ট্রেট (পরবর্তীকালে ডরোথি পেইন হুইটনি এল্মহার্স্ট) দীর্ঘ পঁচিশ বছর শ্রীনিকেতনে আর্থিক সহায়তা দিয়ে গেছেন।
গ্রামীণ মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ কালীমোহন ঘোষ ছিলেন নিভৃতাচারী। সেজন্যেই হয়ত তাঁকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা কোথাও তেমন হয়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছাপ্পান্ন। তবে স্বাস্থ্যের কারণে ১৯৩৯-এর ২২শে নভেম্বর তিনি যে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, একথা প্রভাতকুমারের লেখা থেকেই জানা যাচ্ছে। কালীমোহন ঘোষকে বাঙালি তেমন না চিনলেও তাঁর দুই পুত্রের নাম তো সকলেই জানবেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ ও ‘দেশ’ পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে চেনেন না, এমন সংস্কৃতি-মনষ্ক বাঙালি কোথাও আছেন কিনা সন্দেহ। শান্তিদেব নামটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া (কালীমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শান্তিময় রেখেছিলেন; শান্তিময় আর সাগরময়)। কালীমোহনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিদেবকে যে চিঠিটি লেখেন সেটি এইরকম-‘তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাছে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভঙ্কর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে।’
পরপর তিনজন প্রিয়তম মানুষের চলে যাওয়া। অভ্যস্ত ছিলেন তিনি এসবে, আযৌবন, আমৃত্যু। কিন্তু সভ্যতার পৃথিবীর এমন বিকৃত রূপ দেখার জন্য তো কখনোই প্রস্তুত ছিলেন না। কালিম্পঙে বসে খবর পাচ্ছেন কবি, জার্মান বাহিনী তখন ফ্রান্সের অনেকটাই দখল করে ফেলেছে। গৌরীপুর ভবনে তখন মৈত্রেয়ী দেবীরাও এসেছেন। তখন রোজ সবাই মিলে রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনতেন। মাদমোয়াজেল বসনেক নামের একজন ফরাসী মহিলা তাঁদের সঙ্গে তখন থাকেন। তাই ফ্রান্সের এই দুর্দিনে সকলেই খুব উদ্বিগ্ন। ফ্রান্সের খবর বিশেষ মনোযোগ সহকারে শোনা হতো।
একদিনকার ঘটনা ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ থেকে তুলে দিচ্ছি-
‘সেদিন গুরুদেবের শরীরটা ক্লান্ত ছিল, চুপচাপ বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ দরজার কাছে উত্তেজিত অথচ মৃদু করুণ কণ্ঠস্বরে ‘গুরুদেব’ বলে মাদমোসেল ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন,-“গুরুদেব, আজ ওরা প্যারিসে ‘ডাকঘর’ অভিনয় করছে এখন।”
‘উনি উঠে বসলেন। বেশ বুঝলুম মনের ভিতরে একটা নাড়া লাগল। “আজ? আজ ওরা ‘ডাকঘর’ অভিনয় করছে?” একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে পড়লেন, শুধু উত্তেজিতভাবে পা নড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে বললেন,-“সেবারও রাশিয়াতে ওদের দারুণ দুঃখের দিনে ওরা বার বার অভিনয় করেছে King of the Dark Chamber।”’

এখানে সেদিন অর্থাৎ যেদিন নাৎসি বাহিনীর হাতে প্যারিসের পতন হল। তারিখটা ১৪ই জুন, ১৯৪০। শয়তানের করালথাবায় ধরাশায়ী হয়েছে শিল্পকলার রাজধানী। বসনেকের কাছ থেকে কবি ‘ডাকঘর’ অভিনয়ের যে খবরটি পান, সেটার কথা অনেক জায়গাতেই লেখা হয়েছে। কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসনের বই থেকে জেনেছি, প্যারিসের পতন তখন অবশ্যম্ভাবী, শত্রুপক্ষের হাতে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করার আগের রাতে প্রচারিত হল শেষ রেডিও ব্রডকাস্ট। সেইটিই ছিল ‘The Post Office’-এর ফরাসী অনুবাদের নাট্যাভিনয়। ধ্বংসলীলার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই ধ্বংসকেই যেন সাদরে বরণ করে নেওয়া। অনুবাদটি করেছিলেন ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ, যিনি ১৯৪৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।
এমন বিরল সম্মান পেয়ে সেদিন কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মানব-দরদী মহামানবের কাছে মানবতার এমন ভূলুণ্ঠন সেই সম্মানের আনন্দকেও ম্লান করে দিয়েছিল। কবির তখন কেবলই মনে পড়ছে, একদিন পশ্চিমের মানুষ তাঁকে কীরকম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিল। যে জার্মানিতে তাঁর হাঁটবার পথে ফুল ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল, ব্যাভেরিয়ার রেস্তোরাঁতে তিনি ঢুকতেই সকলের উঠে দাঁড়ানো, যে হাঙ্গেরিতে মানুষ উপচে পড়েছিল শুধু তাঁকে দেখবে বলে, তাদের এই ফ্যাসিবাদী নখ-দন্ত প্রদর্শন তিনি কোনোভাবেই সেইসব দিনের সাথে মেলাতে পারছিলেন না।
তবে এখানে মৈত্রেয়ী দেবী যে দিনগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে এটা নিশ্চিত, যে প্যারিস পতন, ডাকঘর অভিনয়ের সময়ে তিনি কবির কাছে গৌরীপুর লজেই ছিলেন। কিন্তু ‘স্বর্গের কাছাকাছি’তে কবি মৈত্রেয়ীকে একটি চিঠি লিখছেন, সেখানে বলছেন-‘কিছুদিন পরে তুমি আসতে পারবে এ খবরটা এখনকার যুদ্ধের খবরের চেয়ে ভালো। বাঘ শিকারের মতো কোনো adventure-এর বই থাকে তো সঙ্গে এনো-হয়তো এখনকার লেখার কাজে লাগবে।’ চিঠির তারিখ দেওয়া রয়েছে ১৫ই জুন, ১৯৪০। এখানে বেশ গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য চিঠিতে তারিখ দিতে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয়ে যেত আর মৈত্রেয়ী নিজেও সবসময় হিসেব রাখতেন না, এটাও লেখিকা স্বয়ং স্বর্গের কাছাকাছি-তে অনেক জায়গায় লিখেছেন। ফলে এখানেও চিঠির তারিখটি কিছুদিন আগেকার বলেই ধরে নেওয়া ভালো। সেসময় রবীন্দ্রনাথ ‘ছেলেবেলা’ লিখছিলেন।
প্যারিসের পতনের পরদিন ১৫ই জুন এই বাড়িতে বসেই রবীন্দ্রনাথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্টকে টেলিগ্রাফ করলেন। আমেরিকা তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু মিত্রশক্তিকে সেনা ও প্রয়োজনীয় রসদ জোগান দিয়ে চলেছে নিয়মিত। কবির মনে হয়েছিল, এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বুঝি একমাত্র থামাতে পারে আমেরিকাই। রুজভেল্টকে তিনি লিখছেন-“All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics, which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail her mission to stand against the Universal disaster that appears so imminent.”
কবির ভাবনা পুরোপুরি সঠিক ছিল, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না। একথা সত্যি যে, সেই সময়ের সাপেক্ষে আমেরিকার সাহায্য ছাড়া ফ্যাসিবাদ-দমনকে নিতান্ত অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, কারণ ফ্রান্স ততদিনে জার্মানির পদানত, আরেক মহাশক্তি রাশিয়া তখন জার্মানির সাথে অনাক্রমণ চুক্তিতে নিরপেক্ষ ভূমিকায়, বাকি রইল ব্রিটেন, যে নিজেই তখন বিশ্বব্যপী নিজহস্তে গড়া ঔপনিবেশিক দুর্গ সামলাতে টলমল করছে। তবে আমেরিকাকে ‘last refuge of the spiritual man’ বলাটা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ যুদ্ধ যত এগিয়েছে, তত বিশ্ব দেখেছে আমেরিকার স্বরূপ, যার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে হিরোশিমা-নাগাসাকির ঘটনায়। অবশ্য কবি যেসময় লিখছেন, তখন আমেরিকার এই মানব-বিধ্বংসী সত্তার কোনও প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাননি (জাপানি সেনার পার্ল হারবার আক্রমণ ও ফলস্বরূপ আমেরিকার যুদ্ধঘোষণা তাঁর মৃত্যুর ঠিক চারমাস পরে), তাও ধুরন্ধর মহাশক্তিধর জাতির কাছে শান্তি কামনা করাটা ঠিক যেন তাঁর দূরদর্শিতার সঙ্গে যায় না। যেখানে যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পরেই মংপু থেকে ব্যক্তিগত সাহিত্য-সচিব অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন-“…যে পক্ষই হোক উপস্থিতমতো একটা ফল পাবে যাকে সে বলে জিত। তার পরে চলবে সেই কাঁটা গাছের চাষ যা মনুষ্যত্বকে বিক্ষত করবার জন্যে। সেই জন্যেই বলি এ-পক্ষেরই জয় হোক আর ও-পক্ষেরই জয় হোক জয় কামনা করব কার। জয় যে হিংস্র শক্তির।”
এ চিঠিতে অবশ্য আমেরিকা নয়, ইংরেজের শতাব্দীপ্রাচীন শোষক-প্রবৃত্তিকেই পরিষ্কার ইঙ্গিত করেছেন। আসলে কবি চেয়েছিলেন, এই মারণলীলার দ্রুত অবসান, অন্তত জীবদ্দশায় সেটাই দেখে যাওয়া তাঁর অভিপ্রায় ছিল। তাইই হয়ত এই ডেসপারেশন। কিন্তু কাব্যিক বাণী যুদ্ধবাজ রাজনীতিকের কাছে কোনওরকম মূল্য পাবে না, এ তো জানাই কথা। তার প্রমাণ তো কবি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালেই পেয়েছিলেন। জাতির সংজ্ঞা বলতে গিয়ে কবি তখন বলেছিলেন-“It (Nation) has also a political side, but this is only for a special purpose. It is for self-preservation. It is merely the side of power, not of human ideals. And in the early days it had its separate place in society, restricted to the professionals. But when with the help of science and the perfecting of organization this power begins to grow and brings in harvests of wealth, then it crosses its boundaries with amazing rapidity. For then it goads all its neighbouring societies with greed of material prosperity, and consequent mutual jealousy, and by the fear of each other’s growth into powerfulness.”
পাশ্চাত্য শক্তিশালী জাতির যোদ্ধৃভাব, উগ্র জাতীয়তাবাদ, পরজাতি-পীড়নের উদ্দেশ্যে তাঁর চাবুকটি ছিল-“But, you say, “That does not matter, the unfit must go to the wall— they shall die, and this is science.”” ফলাফল, ইংল্যান্ড আর আমেরিকায় ব্যানড হল ‘Nationalism’। কেন? কারণ, এই বই তরুণ প্রজন্মকে যুদ্ধবিমুখ করবে। জাপানেও ঠিক একই কারণে তাঁর প্রচারিত শান্তির বাণীকে ‘পরাজিত জাতির কবির বাণী’ বলা হয়েছিল। সেজন্যেই, এতকিছুর পরেও তিনি শুধু যুদ্ধের সমাপ্তি চেয়ে রুজভেল্টকে চিঠি লিখলেন, এটা একটু মেনে নেওয়া কষ্টকরই।
গৌরীপুর ভবনের ওই বিষণ্ণ-চত্বরে দাঁড়িয়ে তখনও এতকিছু আমি জানতাম না। এখন লিখতে বসে যখন জানতে পারছি, তখন মনে হচ্ছে, শুধু ওই লাইভ ব্রডকাস্টই নয়, আরও কত ঐতিহাসিক মুহূর্ত ধরে রেখেছে এ বাড়ি। জীবন-পথিক কবির জীবনের শেষ ভ্রমণ সফরের সাক্ষীও তো এই বাড়িই। সেসব খণ্ড খণ্ড ইতিহাস-ফ্রেস্কো বোধহয় এখনও লেপ্টে থাকে নোনা-ধরা দেওয়ালের গায়ে। চোখে পড়ে না।
৪.
শেষ প্রহর

৭ই অগাস্ট, ১৯৪০। বাংলা ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৭। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে ডি. লিট. সম্মান দেওয়া হল বিশ্বকবিকে। এই অনুষ্ঠান পালিত হল শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে। সেই অনুষ্ঠানে মৈত্রেয়ী দেবীও এসেছিলেন, তাঁর ভাগ্নী রেণুকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা থেকেছিলেন শ্যামলী গৃহে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। মরিস ছিলেন উদয়নে এবং রাধাকৃষ্ণন উঠেছিলেন পুনশ্চতে। উত্তরায়ণ কমপ্লেক্সের গঠন-পরিকল্পনা দেখে যার-পর-নাই মুগ্ধ হয়েছিলেন মরিস। সম্মান গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য রাখেন তার বেশিরভাগ অংশ জুড়েই ছিল বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার সামনে দাঁড়িয়ে মানবতার প্রতি আশাবাদ-চেতনার অঙ্গীকার।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই সম্মানপ্রদানের সার্থকতা সম্পর্কে লিখেছেন-“এ কথা অতি সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ সম্মান না পাইলে, তাঁহার কিছু অগৌরব হইত না, পাওয়াতেও বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি পাইল না; তবে দেশের দিক হইতে ঘটনাটি তুচ্ছ নহে। কারণ, প্রতীচ্যের এক প্রভু-জাতির অতি রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রাচ্যের এক কবিকে সম্মান দান করিয়া তাঁহার বৈদগ্ধ্য স্বীকার করিয়া লইলেন।”
সেইদিন কেউ দূরতম কল্পনাতেও হয়ত ভাবেননি, ঠিক আর একবছর বাদেই মৃত্যুঞ্জয়ী কবি পাড়ি দেবেন অমৃতলোকে। স্বাস্থ্য অবশ্য তাঁর ভেঙে পড়েছে অনেকটাই তখন। মেজাজেও পরিবর্তন এসেছে। বার্ধক্যের খুঁটিনাটি চিহ্ন ধরতে শুরু করেছে চির-নবীন মানুষটির শরীরে। বরাবরের মিতভাষী লোকটি তখন একটু খিটখিটেও হয়ে গিয়েছিলেন। আর অসম্ভব জেদী। সামান্য ব্যাপার নিয়েও জেদ করছেন সেসময়। প্রতিমা দেবী লিখছেন-“ইদানীং যদি তাঁর কোনো একটা ঝোঁক চাপত কিংবা কোনো বিষয় নিয়ে তিনি হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তখন আর কারুর কথায় কান দিতেন না, কেবল আমার স্বামী (কবির জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এসে যদি বোঝাতেন তখন শিষ্ট ছেলের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন।”
অগাস্ট মাসের শেষে অসুস্থ প্রতিমা দেবী কালিম্পঙে চলে গেলেন হাওয়াবদল করতে। তিনি সেইসময় পায়ে সায়াটিকার যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। রথীন্দ্রনাথ গেলেন পূর্ববঙ্গের পতিসরে, জমিদারি দেখাশোনা করার উদ্দেশ্যে। ৩রা সেপ্টেম্বর আশ্রমে বৃক্ষরোপণ আর বর্ষামঙ্গল একসাথে পালিত হয়েছিল। এই সময় আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পটি লেখেন। ছেলে-বউমা চলে যাওয়ার পর থেকেই কবির মন যাই-যাই করতে শুরু করে। কিন্তু শরীরের কারণে যাওয়া কতটা সম্ভব হবে সে বিষয়ে নিজেই সন্দিহান ছিলেন।
যেদিন বর্ষামঙ্গল উদযাপিত হল, সেইদিনকার চিঠিতে প্রতিমা দেবীকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, মধ্য-সেপ্টেম্বরেই তিনি কালিম্পঙের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। প্রতিমা দেবী তখন একরাতের জন্য মংপুতে থেমেছিলেন। চিঠিতে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য কবির ব্যাকুলতা স্পষ্ট-“হংসবলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানস-সরোবরের দিকে। মংপুতে মাগুরমাছের সরোবর-তীরেও হয়তো শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য-সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম।” মাগুরমাছের সরোবর অর্থাৎ মংপুর বাংলোর বাগানের মধ্যে দিয়ে তির-তির করে একটা ঝর্ণা বয়ে যেত, সেখানে মৈত্রেয়ী দেবী একটা ছোট জলাশয় বানিয়েছিলেন। সেখানে রথীন্দ্রনাথের পাঠানো কিছু কই আর মাগুর মাছ ছাড়া হয়েছিল।
যাওয়ার দিন উপস্থিত হল। সম্ভবত ১৫ই সেপ্টেম্বর। সম্ভবত কেন, সেটা পরে বলছি। সেবার শান্তিনিকেতনে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। অনাবৃষ্টি চলছে। মাটি ফুটিফাটা। বৃষ্টির দেখা নেই। মৈত্রেয়ীকে চিঠিতে লিখছেন-‘বঙ্গীয় সমতট অত্যন্ত অসহ্য।’ রানী চন্দের লেখাতেও পড়েছি-“মাঠ ঘাট ফেটে চৌচির। ধকধক জ্বলে দিগন্তে হাওয়া। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটল। বর্ষা এই আসে এই আসে আশায় দিন কাটাতে লাগলেন গুরুদেব। এক-এক দিন এমন হয়-মেঘ করে আকাশ ছেড়ে, গুরুগুরু গর্জনও করে, কিন্তু কোনো করুণা করে না শেষ পর্যন্ত। আশ্রমের উপর দিয়ে শালবীথির মাথা ডিঙিয়ে মাঠ পেরিয়ে চলে যায় দূরে কালো মেঘ অতি অবহেলায়। সবাই চেয়ে থাকি আকাশের দিকে, যে, আজ বৃষ্টি হবেই, মেঘের পর মেঘ ঐ আসছে এগিয়ে, এল এল, এই বর্ষা ঝরে পড়ল; আগ্রহে উল্লাসে ছুটোছুটি করি অঙ্গনে-ক্ষণেক পরেই মলিন মুখে ঘরে ঢুকি। এই প্রহসনই চলতে থাকল রোজ।”
এমনিতে পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়ার চেয়ে রাঢ়বঙ্গের বর্ষাকেই কবির পছন্দ ছিল বেশি। কিন্তু সেবারে এইরকম ভয়ঙ্কর গরমের কারণেই বোধহয় অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও কালিম্পং চলে যেতে চাইলেন। দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন দিনকে দিন। সেদিনকার, অর্থাৎ সম্ভাব্য ১৫ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা রানী চন্দের লেখায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে। বোলপুর থেকে যাবেন কলকাতায়। তখন বোলপুর স্টেশন বড়ও ছিল না, ব্যবস্থাপনাও উন্নত ছিল না। আশি বছরের রবীন্দ্রনাথকে যাতে বেশি কষ্ট করতে না হয়, সেজন্য আগে থেকে স্টেশন-মাস্টারকে বলা থাকত যাতে সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্মেই ট্রেন দেওয়া হয়। এছাড়া মাল-পরিবহনের জন্য একটা ছোট গেট ছিল স্টেশনের একধারে। সেই গেট অবধি চলে যেত কবির গাড়ি। ট্রেনও একদম গেটের কাছাকাছি প্ল্যাটফর্মের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ত। তবে শুধু গুরুদেব তো নয়, তাঁর সঙ্গের লটবহর, লোকজন, সেসবের সংখ্যাও নেহাত কম হতো না। জিনিসপত্র ব্যবহার করতেন খুব কম, কিন্তু খুঁতখুঁতে ছিলেন বড় বেশি, আর চরম খামখেয়ালি। তাই সেক্রেটারিদের কালঘাম ছুটে যেত সুষ্ঠু ব্যবস্থাদি করতে করতে। সেদিনও ওরকম চলে গেছেন। রানীর মন একটু খারাপ। কোনার্ক বাড়ির ছাদে ছিলেন পুত্র অভিজিতকে। হঠাৎ দেখেন, তাঁর গুরুদেবের মোটর ফেরত আসছে গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে। ফেরত আসার কারণ হচ্ছে, ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে ওইরকম একটুকরো মেঘের সাক্ষাৎ।
এবার কেন সম্ভাব্য ১৫ই সেপ্টেম্বর বলছি সেবিষয়ে বলি। রানী চন্দের লেখায় রয়েছে-“সেই মেঘও কিন্তু জল হয়ে নামল না শেষ পর্যন্ত। দু-তিন দিন পরে আবার রওনা হতে হল গুরুদেবকে। এবারে সত্যিই গেলেন কালিম্পঙে। সেই সেবারেই-যেবারে অসুস্থ হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়।” এখানে ওই রবীন্দ্রনাথের স্টেশন থেকে ফিরে আসার দিনটির কোনও তারিখ উল্লেখ করেননি রানী। আর ‘রবীন্দ্র জীবনী’তে প্রভাতকুমার লিখেছেন-“সকলের বাধা ও নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সুধাকান্তকে লইয়া কবি কলিকাতা চলিয়া গেলেন (১৭ সেপ্টেম্বর), পাহাড়ে যাইবেনই।” এখান থেকেই আমার অনুমান, সেদিনটা হয়ত ১৫ই সেপ্টেম্বর হবে।
যাত্রার শুরুতেই এরকম বাধা পড়েছিল সেবার। তার উপর শরীরের দিক দিয়েই শুধু নয়, মনের দিক দিয়েও কবি যেন বল পাচ্ছিলেন না। ১৯ তারিখ রওনা হবেন। তার আগেরদিন প্রশান্ত মহলানবিশ যখন জোড়াসাঁকোয় দেখা করতে যান, তাঁকে বলেছিলেন-‘প্রশান্ত পাহাড়ে তো যাচ্ছি কিন্তু কেন জানি না আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছে এই যাওয়াটা আমার শুভ হবে না, একটা বিপদ ঘটবে।’ প্রশান্তর স্ত্রী রানী তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে গিরিডিতে, তাঁর মায়ের কাছে। প্রশান্ত ১৮ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে রানীকে লিখছেন-“কেন উনি এরকম বললেন জানি না, কিন্তু ওঁর এই মন খারাপ করে যাওয়া দেখে আমারও খারাপ লাগছে। কেন এত মন খারাপ করে বাড়ি থেকে বেরোলেন, তার চেয়ে বোধহয় না গেলেই হতো।”
কবির দুজন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার দুজনেই তাঁকে নিষেধ করছিলেন পাহাড়ে যেতে। তাও তাঁর জেদাজেদির কাছে অবশেষে হার মানেন। কালিম্পঙে তাও হাসপাতাল রয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে (টেলিফোনের উদ্বোধন তো স্বয়ং কবির হাতেই হয়েছিল) তাই তাঁরা নিমরাজি হয়েও মত দেন যে গেলে কালিম্পং ঠিক আছে, তবে মংপু একেবারেই নয়। এদিকে মৈত্রেয়ীকে কথা দিয়েছেন মংপু আসবেনই। সেজন্যে মৈত্রেয়ীর মা হিমানী দেবী মেয়েকে চিঠি লিখে বলেছিলেন কবিকে যেকরে হোক বারণ করে পাহাড়যাত্রা থেকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু নিয়তির টানও অমোঘ আর মানুষ রবীন্দ্রনাথও মরণশীল, অতএব ১৯ সেপ্টেম্বরের দার্জিলিং মেলে যাত্রা করলেন কবি, শেষবারের মতো।
গৌরীপুর লজ ‘আসবাবশূন্য নিরলঙ্কার-এখানে কেউ কোনো দিন বাস করেছে বলে মনে হয় না’। এখন মানুষ বাস করে, তবে ‘নিরলঙ্কার’ থেকে ক্রমশ ‘নিরাকার’ হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে এলে বেশ অনেকগুলো ঘর ব্যবহার করতেন। সুবিশাল অট্টালিকায় ঘরের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। কিন্তু কোন ঘরগুলো ব্যবহার করতেন তিনি? প্রতিমা দেবীই বা কোন ঘরে থাকতেন? কবির একটি আলাদা বসবার ঘর ছিল। মৈত্রেয়ী দেবীরা এলে সেই ঘরের পাশের ঘরে থাকতেন। সেগুলোই বা কোনগুলো? সঞ্জিতা দেখাতে পারেননি। এজন্য তাঁকে দোষ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এত খুঁটিনাটি কথা তাঁর জানার কথা নয়। যেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁইয়েরই ভেঙে পড়বার উপক্রম, সেখানে একসময়ে রবীন্দ্রনাথ এসে কোন ঘরে থাকতেন, এসব জেনে তাঁর লাভ কী!
১৯ তারিখ রওনা হয়ে ২০ তারিখ এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। প্রতিমা দেবী লিখছেন-“উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শুনি হর্ন বাজাতে বাজাতে প্রকাণ্ড মোটরটা পাহাড়ের সরু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে। গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল; আমরা এগিয়ে গেলুম, সুধাকান্ত দেখলুম আগেই নেমে পড়েছে তারপর বাবামশায়কে হাত ধরে নামিয়ে দিলে। তাঁকে এবার খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল।” এখানে এই যে সরু রাস্তাটার কথা বলেছেন, সেটা কী এই সামনের এবড়োখেবড়ো রাস্তাটাই যেটার মুখে আমাদের কোয়ালিশ দাঁড়িয়ে গেল! তাইই হবে। এখন এখান দিয়ে গাড়ি নামবার কোনও উপায় নেই অথচ তখন প্রকাণ্ড মোটর নামত দিব্যি। তার মানে এখন যা সরু, তার চেয়ে বেশ খানিক চওড়া ছিল তখন। অবশ্য রাস্তাটাকে দেখলেই মনে হবে, ডানদিকের অংশটা ধ্বসে গেছে বহুদিন।
সুধাকান্ত রায়চৌধুরিকে কবি নিজেই জোরাজুরি করে পাঠিয়ে দেন শান্তিনিকেতনে, কারণ তাঁর ছেলে তখন অসুস্থ ছিল। তাঁর পার্সোনাল অ্যাটেন্ডেন্ট সচ্চিদানন্দ রায় ওরফে আলুবাবু শুধু থেকে যান। প্রথম কদিন ভালোই ছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে লিখছেন-“কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত।” অমিয়কে আসতেও বলে দেন কবি, কারও চিন্তাতেই তখন এ ভাবনা আসেনি, যে কী ভয়ঙ্কর সময় অপেক্ষা করে আছে।
২৬শে সেপ্টেম্বর মংপু থেকে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর মেয়ে ও ভাগ্নীকে নিয়ে এলেন। তাঁকে ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পটা পড়ে শোনাবেন খুব সাধ ছিল গল্পকারের, কিন্তু শরীরের অবস্থার কারণে পেরে উঠলেন না। সেজন্য তাঁকে গল্পের খাতাটা দিয়ে বললেন নিজেই পড়তে। মৈত্রেয়ীকে কৌতুক করে বললেন-‘এসেছিলে কাব্যচর্চা করতে, পড়ে গেলে রোগ পরিচর্যায়। এখন, সেখানে কি হবে?’ নিজের অসুখ করলেও অপরের জন্য চিন্তা করা তাঁর সহজাত স্বভাব ছিল।
গৌরীপুর ভবন বাড়িটার একটা ব্যাপার ছিল, সেটা হচ্ছে, পাহাড়ি অঞ্চলে যেরকম কাঠের বাড়ি তৈরি হয়, সেরকম কাঠের ছিল না, ছিল সিমেন্টের। তাই ঠাণ্ডাভাবটাও হতো বেশি। আর রবীন্দ্রনাথও জানলা খুলে দেওয়ার জন্য জেদ করতেন বলে চারপাশ খোলা থাকত। তাই বৃদ্ধ মানুষের ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। মৈত্রেয়ীরা যেদিন এলেন, সেদিন থেকেই শরীরটা খারাপ করতে শুরু করল। দুপুরে পড়ে গিয়েছিলেন চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে।
সেই দুদিনের অভিজ্ঞতা বারবার পড়েছি। তাঁর কঠিন সময়ে পাশে থাকা তাঁর কন্যাসমা দুই নারীর লেখনী আমার কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে। প্রতিমা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবী দুজনের বর্ণনাতেই অনুভব করেছি, সেই যুগে ওইরকম পাহাড়ের কোলে দুর্যোগের রাতে অচৈতন্য রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কী অসহায়ত্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিমা দেবী নিজে তখন অসুস্থ। তবু মৈত্রেয়ী দেবীর মতো করিৎকর্মা মানুষ ছিলেন বলে কিছুটা হলেও সুবিধা হয়েছিল।
২৬ তারিখ বিকেলে কালিম্পঙের বাঙালি ডাক্তার গোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং স্কটিশ ডাক্তার ক্রেগ এসে দেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ইউরেমিয়া রোগের সংক্রমণের ফলে কবি অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। গোপাল দাশগুপ্ত কবির বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখ এই দুজনের লেখাতে তো পেয়েইছি, পেয়েছি প্রবোধ সান্যালের লেখাতেও। ওই যেখানে শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে করে কালিম্পঙে যাওয়ার কথা লিখেছেন, সেইবারের সফরেই গোপাল দাশগুপ্তের বাড়িতে দিনদুয়েকের অতিথি হয়েছিলেন প্রবোধকুমার। কালিম্পঙের অভিজাত বাঙালি পাড়ায় তাঁর বাড়ি ছিল। ডাক্তার ক্রেগের নামটি কেবল ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ‘নির্বাণ’-এ তাঁকে কেবলমাত্র ‘হাঁসপাতালের ডাক্তারসাহেব’ বলেই উল্লেখ করেছেন প্রতিমা দেবী। এখানে হাসপাতাল বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে, সেটি হচ্ছে ওই স্কটিশ মিশনারিদেরই তৈরি করা হাসপাতাল। আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে, কালিম্পঙের এক ও অদ্বিতীয় জন আলেকজান্ডার গ্রাহাম ও তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৈরি হাসপাতাল। কালিম্পঙের ইতিহাসের পাতায় পাতায় যেন মিশে আছেন তাঁরা।

এখানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটিও অল্প করে বলে দিচ্ছি। সেইসময় কালিম্পঙে কোথাও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। অসুস্থ মানুষজনকে অনেকটা পথ পেরিয়ে যেতে হতো দার্জিলিঙের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ডিসপেনসরি অথবা লোয়িস স্যানিটোরিয়ামে। ১৮৯০ সালে কালিম্পং মিশন চত্বরে এক শিক্ষকের বাড়ি ভাড়া নিয়ে তৈরি হয়েছিল ছোট্ট ডিসপেনসরি। স্থানীয় একজন নার্স ও সামান্য কিছু চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিয়ে চালু করেছিলেন ক্যাথরিন গ্রাহাম নিজেই। মাত্র দুটি ঘরে চার থেকে পাঁচজন রুগীর স্থান সঙ্কুলান হতো। ১৮৯২ সালের ১৯শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে পথচলা শুরু হয়েছিল হাসপাতালের। উদ্বোধন করেছিলেন বিশিষ্ট স্কটিশ টি প্ল্যান্টার জর্জ ডব্লিউ ক্রিস্টিসন। জর্জের আরও একটা পরিচয় আছে। দার্জিলিং-সিকিম অঞ্চলের প্রথম মানচিত্রটি তাঁর হাতেই অঙ্কিত হয়। হাসপাতালের খরচ চালাবার দায়িত্ব নেয় ব্রিটিশ সরকার এবং চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের জেনারেল অ্যাসেম্বলির মডারেটর প্রফেসর আর্চিবল্ড হ্যামিল্টন চার্টেরিসের স্থাপিত ‘উইমেন’স গিল্ড’। এডিনবরা মেডিক্যাল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর চার্লস ফ্রেডেরিক পন্ডার ছিলেন এই হাসপাতালের প্রথম ডাক্তার। পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল হয়ে ওঠার আগেই ১৮৯৩-এর অক্টোবরে ছোট ডিসপেনসরিতে বসেই একাহাতে ১৫৮৮ জন রুগীর চিকিৎসা করেছিলেন চার্লস পন্ডার, এমন রেকর্ড আছে। ১৮৯৪ সালের প্রথম দিকে হাসপাতালের নামকরণ করা হয় প্রফেসর চার্টেরিসের নামেই। সেবছরই সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এই হাসপাতাল। পরের বছর ৩০শে এপ্রিল প্রথম নার্স হিসাবে এলেন ডক্টর চার্লসেরই বোন মিস অ্যান পন্ডার। রেকর্ড অনুযায়ী, প্রথম বছরে হাসপাতালের আউট-পেশেন্ট ডিপার্টমেন্টে মোট ৭৭০৪ জন মানুষের চিকিৎসা হয়েছিল। পন্ডার ভাইবোন সবসুদ্ধ ১৩৪৪৬ জন রুগীর চিকিৎসা করেছিলেন। পন্ডার স্থানীয় যুবকদের কম্পাউন্ডিং শিক্ষা প্রদান করতেন, আর তাঁর বোন, শ্রীমতী গ্রাহাম ও একজন বাঙালি নার্সের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার। হাসপাতালের প্রথম কম্পাউন্ডার ছিলেন লেপচা-খ্রিস্টান যুবক দিংবু। ১৮৯৮ সালে পন্ডাররা চলে যাওয়ার পর তাঁদের জায়গায় এসেছিলেন ওই এডিনবরা মেডিক্যাল স্কুলেরই ডাক্তারির ছাত্র উইলিয়াম রয় ম্যাকডোনাল্ড এবং নার্সিংয়ের মিস জিনি ক্যাম্পবেল। ১৯০৪ সালে অপারেশন থিয়েটার চালু হয়। তিব্বত, সিকিম থেকেও মানুষজন চিকিৎসার জন্য আসতেন। ১৯৭২ সালে পুরনো ভবনটি ভেঙে ফেলে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় নতুন ভবন তৈরি হয়। নাম হয় কালিম্পং সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল। এখন যেহেতু কালিম্পং আলাদা জেলা, তাই এখন এটি জেলা হাসপাতাল।
ক্রেগ সম্ভবত তখন চার্টেরিস হাসপাতালের নতুন চিকিৎসক। বয়স তখন বেশ কম। তাঁর পুরো নাম কোথাও পাইনি। তাঁকে রবীন্দ্রনাথের বেশ পছন্দ হয়েছিল এটা প্রতিমা দেবী লিখেছেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর বেলার দিকে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লে মৈত্রেয়ী দেবী মংপু ও কলকাতায় যোগাযোগ করার সমস্ত ব্যবস্থা করেন। গৌরীপুর ভবনের পাশের বাড়িতে টেলিফোন ছিল। সেখান থেকে আলুবাবু শান্তিনিকেতনে অনিল চন্দকে ফোন করে সব কথা জানান। পাশের বাড়িটি ছিল কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী শরৎচন্দ্র বসাকের। কলকাতায় বিশ্বভারতীর অফিসে ফোন করে কবির অসুস্থতার খবর জানানো হয়। প্রতিমা দেবী নিজে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে প্রশান্ত মহনানবিশকে ফোন করেন। তারপর প্রতিমা দেবীর নির্দেশে মৈত্রেয়ী দেবী গাড়িতে করে একাই চলে যান কোনোভাবে রথীন্দ্রনাথের কাছে পতিসরে যদি খবর পৌঁছনো যায়, সেই ব্যবস্থা করতে। প্রতিমা দেবীর আরও নির্দেশ ছিল, কোনো বড় ডাক্তার যদি এইসময়ে আসতে পারেন, তাহলে সেই ব্যবস্থাও যেন মৈত্রেয়ী করেন। কারণ, ডাক্তার দাশগুপ্ত তখন নিজেই দিশেহারা আর ক্রেগও “সার্জিক্যাল কেস হাতে নিতে বড়ো ইচ্ছুক নন, বোধ হয় ভয় পেয়েছিলেন।”
তবে প্রতিমা দেবীর জানার কথা নয়, যে আসলে ভয় নয়, ক্রেগের না আসার কারণ ছিল সম্পূর্ণই পেশাদারি। সেটা মৈত্রেয়ী দেবী জানিয়েছেন। চার্টেরিস হাসপাতালের অবস্থান ছিল বাজার পার হয়ে উঁচু পাহাড়ের গায়ে। ডাক্তারের বাড়িও ছিল সেখানেই। সাজানো বাগানঘেরা। মৈত্রেয়ী যখন তাঁকে আসবার জন্য অনুরোধ করেন, তিনি বলেন হাসপাতালে এক প্রসুতি মহিলার প্রসব হবে, সুতরাং অসুস্থ মানুষটি নোবেলজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেও তাঁর পক্ষে এখন যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব পেশেন্টও নন। অনেক অনুরোধেও রাজি না হলে মৈত্রেয়ী দেবী প্রায় তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করেন। সেই যুগে বাঙালি ঘরের বউদের পক্ষে যা একপ্রকার অসম্ভব তো বটেই, রক্ষণশীল সমাজের চোখে অপরাধও বটে। কিন্তু সঙ্কটময় অবস্থায় বুঝি সেসব সংস্কারের বেড়াজাল স্রেফ ভেঙে যায়। লেখিকা নিজেই বলেছেন-“আমি মানসম্মান বিসর্জন দিয়ে সেই উদ্ধত বিমুখ বিজাতীয় পর-পুরুষের পায়ের কাছে বসে অশ্রুপাত করতে লাগলাম-“Oh! I beg you on my knees!” সাহেব উঠে পড়ে পায়চারি করতে লাগল। লম্বা বারান্দায় তার চিন্তিত ঈষৎ বিচলিত পদধ্বনি আমায় একটু আশ্বস্ত করলো।”
ক্রেগের সম্পর্কে কালিম্পঙে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। সফল হইনি। সেভাবে তাঁর নামও কোথাও পাইনি। তবে অ্যালেক্স ম্যাককের বই থেকে একটা ছোট তথ্য পেয়েছি। অ্যালেক্স ম্যাককে ইন্দো-তিব্বতীয় ইতিহাসে পণ্ডিত, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তথ্যটা হল এই যে, থিম্পুতে একটি হাসপাতাল গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে ভুটানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জিগমি পালদেন দোর্জির আমন্ত্রণে জনৈক ডক্টর পেম্বা ও ডক্টর ক্রেগ কালিম্পং থেকে ভুটানে এসেছিলেন। ক্রেগের সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তিনি এডিনবরা মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেন ও একজন কুষ্ঠরোগ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ভুটানে যেসময় যান, তখন তিনি চার্টেরিস হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট। কালিম্পঙের হাসপাতালে যতজন কুষ্ঠরোগী ভর্তি হতেন, তার অর্ধেকই ছিলেন ভুটানি, সেজন্যে ক্রেগ ভুটানি মানুষদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। অনেক ভুটানি যুবকও তাঁর কাছে ওষুধ-পথ্যির শিক্ষা নিতেন বলে জানা যায়। তবে এই ক্রেগই ‘কালিম্পঙ হাসপাতালের ছোকরা সাহেব ডাক্তার’ কিনা, সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। অবশ্য জিগমি দোর্জির প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়সীমা (১৯৫২-৬৪) দেখলে মনে হয়, এই ক্রেগই তখনকার ক্রেগ, এবং অল্পবয়সী ছিলেন বলে তাঁকে ছোকরা ডাক্তার বলেছেন মৈত্রেয়ী দেবী।
ক্রেগ অবশেষে মৈত্রেয়ীর জেদের কাছে হার মেনে দার্জিলিঙের নামকরা সিভিল সার্জনকে খবর দিয়ে আসতে বলে দিয়েছিলেন। সিভিল সার্জনের নাম প্রতিমা দেবী কিছু উল্লেখ করেননি, মৈত্রেয়ীও ‘ডাক্তার ফ-’ লিখেছেন। ফলে তাঁর নাম পরিচয় জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি ওই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সন্ধে সাড়ে সাতটা কি আটটা নাগাদ এসে উপস্থিত হন। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ শরীর ও মনে বলিষ্ঠ ছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত কবিকে দেখে সার্জন বলে উঠেছিলেন-“What a wonderful body Dr. Tagore has!”
সার্জন এসেই রোগীর অবস্থা দেখে অপারেশন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হাসপাতালে দেওয়া হয়নি কেন, নার্স কে এসব পেশাদারি প্রশ্ন করা শুরু করেন, যেসবের উত্তর দেওয়ার জন্য না প্রস্তুত ছিলেন প্রতিমা, না মৈত্রেয়ী। ডাক্তার দাশগুপ্তও নীরবে অপারেশন করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। কিন্তু সেইসময়ে আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, কাছের মানুষজন নেই, ওই অবস্থায় অপারেশন করানোটা হঠাকারিতা হবে ভেবে দুজনের কেউই অপারেশনে মত দিচ্ছিলেন না। প্রতিমা মৈত্রেয়ীকে বলেন, বাবামশায়ের জ্ঞান থাকলে তিনিও অপারেশনে মত দিতেন না। কিন্তু সাহেব ডাক্তার এদিকে নাছোড়বান্দা। তাঁর কড়া নির্দেশ, রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, অপারেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। নয়ত বারো ঘণ্টায় কী হয়ে যায়, কোনও ঠিক নেই। দুই দেবীর লেখা পড়েই একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের অসুখ হওয়াতে তাঁরা যত না অসুবিধায় পড়েছিলেন, আরও বেশি কঠিন পরীক্ষায় পড়েছিলেন ইংরেজ সার্জনের নাছোড় মনোভাবে। কেন সেই ডাক্তার অপারেশনের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, তার কারণ অবশ্য প্রতিমা দেবী পরে রানী মহনানবিশকে বলেছেন-“সাহেব ডাক্তারের খুব ইচ্ছে যে সে অপারেশন করে-এতবড়ো একটা নামজাদা রুগী তো সে সহজে পাবে না, কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, তুমি যদি অপারেশনে মত না দাও তাহলে জেনো যে ওঁর মৃত্যুর কারণ তুমি হবে।”
যাইহোক, দুজনে কোনোক্রমে সার্জনকে নিরস্ত করতে পেরেছিলেন। কলকাতায় আরেকবার ফোন করে জানা গেল, যে ডাক্তারদের নিয়ে প্রশান্ত মহলানবিশ দার্জিলিং মেলে রওনা হয়ে গেছেন। এই ফোন ডাক্তার নিজেই করেছিলেন। কলকাতার ডাক্তাররা আসছেন জেনে তিনি আর কিছু জোরাজুরি করেননি, তবে বলে গিয়েছিলেন, দরকার হলে ডাকলেই তিনি আবার আসবেন। ডাক্তারের এই উদার মানসিকতার কথা অবশ্য মৈত্রেয়ী দেবী লেখেননি। তাঁর লেখায় ডাক্তারকে একগুঁয়ে, জেদী, দোর্দণ্ডপ্রতাপ বলেই বেশি মনে হয়েছে। প্রতিমা দেবী বরং ডাক্তারের খানিক নরম চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। ইংরেজ ডাক্তার যাওয়ার পর একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এসে কিছু হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে যান। কবির হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক চিকিৎসার ঝোঁক ছিল বলে তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ ওইসব ওষুধ থাকত। হোমিওপ্যাথির গুণে পরদিন ভোরের দিকে তাঁর চেতনা ফিরে আসে। তবে আমার খটকা লেগেছে অন্য একটা বিষয়ে। দুই লেখিকাই লিখেছেন, সেসময়ে তাঁদের সাথে কোনও পুরুষ সহায় নেই। অথচ সেদিন সচ্চিদানন্দ রায়ই বিশ্বভারতীতে ফোন করে খবর জানিয়েছিলেন কালিম্পং থেকে। তিনি তাহলে সেই দুর্যোগের সময়ে কোথায় ছিলেন? কলকাতা থেকে পরদিন সকালে যখন সবাই এসে পড়েন, এবং কবিকে ট্রেনে করে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়, তখনও সঙ্গীসাথীদের মধ্যে সুধাকান্ত রায়চৌধুরি ও অনিল চন্দের নাম পেলেও তাঁর উল্লেখ পাইনি। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই ঠেকে।
পরদিন অর্থাৎ ২৮শে সেপ্টেম্বর সকালে তিনজন ডাক্তার সত্যসখা মৈত্র, অমিয়নাথ বসু ও জ্যোতিপ্রকাশ সরকার (নীলরতন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র) কে নিয়ে এসে পড়েন প্রশান্ত মহলানবিশ ও কবিকন্যা মীরা দেবী। মেয়েকে দেখে কবির চিরন্তন আনন্দ উছলে উঠেছিল। তারপর নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে পৌঁছে দুপুর নাগাদ আসেন অনিলকুমার চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরি এবং তৎকালীন শান্তিনিকেতন সচিব সুরেন্দ্রনাথ কর। মংপু থেকে মনোমোহন সেনও চলে আসেন।
অর্ধচেতন রোগীকে নিয়ে এতজনের দল নামবে রাস্তা দিয়ে। এদিকে আগেরদিনের বৃষ্টিতে পাহাড়ি রাস্তা বহু জায়গায় ধসে গেছে। মনোমোহন সেনের নেতৃত্বে শ’খানেক শ্রমজীবী রাস্তা সারাইয়ের কাজ করেছিলেন। একটু একটু করে রাস্তা সারাই হচ্ছিল, গাড়ি এগোচ্ছিল। গাড়ি বলতে একটি বিরাট স্টেশন ওয়াগন। তার মধ্যে সিট খুলে বিছানা পাতা হয়েছিল। মৈত্রেয়ী দেবী ছিলেন পরিচর্যায়। আমি ভাবছিলাম, এঁদের কথা তো ঠিক আছে, বইতে পাওয়া যাবে, স্বমহিমায় তাঁরা ভাস্বর, কিন্তু সেদিন কবিকে যাতে নিরাপদে নামিয়ে আনা যায়, সেজন্যে ওই একশোজন শ্রমজীবী মানুষ যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলকাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে রাস্তা সারাইয়ের পরিশ্রম করে গেছিলেন, তাঁদের কথা আর কেই বা বলবে! ইতিহাস, সেও বুঝি কেবল সামনে থাকা মানুষদেরই জয়গান গায়।
২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫। আর ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০। কত পার্থক্য দুটো দিনে। অথচ উপলক্ষ্য সেই একজনই। স্থান সেই একই গৌরীপুর ভবন। ২৫শে বৈশাখে সকলের হৃদয়ে ছিল মুগ্ধতা আর ২৮শে সেপ্টেম্বরে সকলে ছিলেন উৎকণ্ঠিত। আর বাড়িটা? সে কি ভাবছিল? সে কি জানত, আর খানিক পরেই চিরতরে তার নাড়ি ছিঁড়ে চলে যাবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর?
৫.
যেটুকু ভাবনায় ছিল

কবির শেষ ভ্রমণসফর। সমাপ্তিটা একেবারেই সুখকর ছিল না। সেবার দুপুর নাগাদ রওনা হয়ে রাত ন’টায় পাঁচ-ছয়খানা গাড়ির ক্যারাভান শিলিগুড়ি এসে পৌঁছয়। পতিসর থেকে ততক্ষণে শিলিগুড়ি পৌঁছে গেছেন রথীন্দ্রনাথ। যে টেলিফোনের মাধ্যমে বেতার সংযোগের উদ্বোধন হয়েছিল কবির হাত দিয়ে, কবির সঙ্কটময় মুহূর্তে সেই পরিষেবাই অসামান্য কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিল। কবির অসুস্থতার খবর জানিয়ে যখন ফোন করা হচ্ছিল, সেই খবর জেনে নিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্মীরা অল ইন্ডিয়া রেডিওকে দেয়। বেতারে কবির অসুস্থতার খবর সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়। রথীন্দ্রনাথ সেটা শুনেই তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি চলে এসেছিলেন। কলকাতায় পৌঁছনোর পর গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই এসেছিলেন মহাত্মাজীর শুভেচ্ছা-বার্তা সঙ্গে নিয়ে।
শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ট্রেন। এইখানে আমার নিজস্ব একটা ভাবনা বড় কাজ করে। আগেই বলেছি, রেলের ইতিহাস আমার অন্যতম ইন্টারেস্টিং বিষয়। সেই সূত্রেই কলকাতা-শিলিগুড়ি রেলপথ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। দেশভাগের আগেকার লাইন। পূর্ববঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া গল্পের টান। শিয়ালদহ-রানাঘাট-ভেড়ামারা-হার্ডিঞ্জ ব্রিজ-ঈশ্বরদি-সান্তাহার-হিলি-পার্বতীপুর-নীলফামারি-হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি। বারো ঘণ্টার যাত্রা। দেশভাগের আশঙ্কা করেননি তখনও কেউ। কেউ ভাবেননি, নিজেদের ‘দ্যাশের ভিটা’য় যেতে একদিন পাসপোর্ট-ভিসার নিয়মকানুন মানতে হবে। ফরাক্কার ভাবনা কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। তারপর ১৯৪৭ থেকে নতুন রুট। এদিকে গঙ্গার ওপর ওরকম হার্ডিঞ্জ ব্রিজের মতো কোনও সেতু নেই। হার্ডিঞ্জ তো তখন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। পদ্মা তখন বিদেশ। তাই শিয়ালদহ থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস গিয়ে পৌঁছত বিহারের সকরিগলির ঘাট স্টেশনে। অত অবধি ছিল ব্রডগেজ। তারপর ফেরিতে গঙ্গা পেরিয়ে উল্টোদিকের মণিহারি ঘাট স্টেশনে। মণিহারি ঘাট থেকে মিটার গেজ ট্রেনে কিষাণগঞ্জ। তারপর আবার ন্যারো গেজে শিলিগুড়ি। এই সবসুদ্ধ যাত্রায় সময় লাগত বাইশ ঘণ্টা। এই বাইশ ঘণ্টার ক্লান্তিকর যাত্রা আর কবির ওই অসুস্থতা নিয়ে আমার বাবা একবার একটা দারুণ মন্তব্য করেছিল-‘১৯৪৯ সালের আগে ভাগ্যিস ঘটেছিল সেই ঘটনাটা। কবিগুরু শেষ যে বার কালিম্পঙে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখনও রাত্তিরে শিলিগুড়ি নামিয়ে আনা হয়। তখন যদি এই বাইশ ঘণ্টা জার্নি হতো তাহলে কী হতো কে জানে!’

আমাদের গৌরীপুর ভবন ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়ে এল। সুদীপ তাড়া দিচ্ছে। অন্যান্য জায়গাগুলো এখনও দেখানো বাকি যে। চলে আসার সময় সঞ্জিতাকে একবার চিত্রভানুর কথা জিজ্ঞাসা করি। প্রতিমা দেবীর ছবি আঁকার স্টুডিয়ো ছিল সেখানে। সাহিত্যেও উল্লেখ পেয়েছি। সেটা কতদূরে এখান থেকে? সঞ্জিতা বলেন, ওটা আরেকটু নীচের দিকে। চিত্রভানু তৈরি হয়েছিল কবির মৃত্যুর ঠিক দু’বছরের মাথায়। এখন যেখানে পাইন ভিউ ক্যাকটাস নার্সারি, ঠিক তার পাশেই চিত্রভানুর গেট। এ জায়গাটার নাম ছিবো বস্তি। গেটের দুদিকে লেখা তারিখ। ২২ শ্রাবণ, ১৩৫০। ৮ অগাস্ট, ১৯৪৩। শেষজীবনে রথীন্দ্রনাথের সাথে যখন তাঁর চির-দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে, সেসময় প্রতিমা দেবী এখানে এসে দিন কাটিয়ে যেতেন। ছবি আঁকতেন। দুই শিল্পীর স্মৃতিতে ভরপুর এই বাড়ি। এখন রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনস্থ নারী শিক্ষা কেন্দ্র এখানে। পাহাড়ি মহিলারা হাতের কাজ শেখেন। উপযুক্ত পথেই ব্যবহৃত হচ্ছে চিত্রভানু। গৌরীপুর ভবনটাও যদি কোনোভাবে ব্যবহৃত হতো।
ইতিহাস নিয়ে চায়ের কাপে তুফান তোলা বাঙালির বুঝি এতটা ইতিহাস-বিস্মৃত হওয়া সাজে না!


তথ্যঋণ:
দেবী, মৈত্রেয়ী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রাইমা পাবলিকেশন, ১৯৪৩।
—-। “এনড্রুজ সাহেব”, রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে, ১৬০-১৬৫, প্রাইমা পাবলিকেশন, ২০০৬।
—-। “বিশ্ব মানব”, রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে, ১০৪-১০৯, (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪)। প্রাইমা পাবলিকেশন, ২০০৬।
—-। স্বর্গের কাছাকাছি, প্রাইমা পাবলিকেশন, ১৯৮১।
ঠাকুর, প্রতিমা। নির্বাণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৪২।
মহলানবিশ, নির্মল কুমারী। বাইশে শ্রাবণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৯।
চন্দ, রানী। গুরুদেব, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬২।
মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী খণ্ড ৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬৪।
দাশ, রমেশ। “তিস্তা উপত্যকা রেলপথ”। আমাদের ছোট রেল, ৫২-৭২, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।
বিশ্বাস, রতন। “নীল নির্জনে ঠায় দাঁড়িয়ে চিত্রভানু”। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই মে ২০১৩।
Dutta, Krishna and Robinson, Andrew. Rabindranath Tagore: The Myriad-minded Man. TPP, 1995.
Sharma, Jayeeta. “Kalimpong as a Transcultural Missionary Contact Zone.” In Transcultural Encounters in the Himalayan Borderlands, 25-54. Heidelberg University Publishing, 2017.
McKay, Alex. “Bhutan: A Later Development.” In Their Footprints Remain: Biomedical Beginnings Across the Indo-Tibetan Frontier, 173-204. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
Tagore, Rabindranath. Nationalism in the West. London: Macmillan, 1917. Online source: Bichitra.
Visva Bharati Official Website





অনেক কিছু জানতে পারলাম, ভালো লাগছে ধারাবাহিকটি
– অলোকপর্ণা